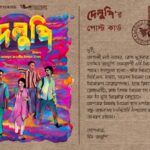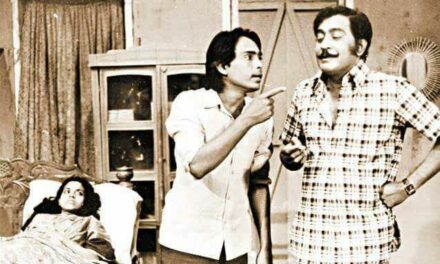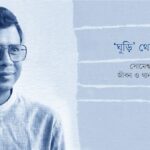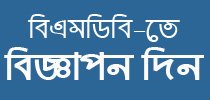কালচারাল তেলুগুবাদ: ‘তুফান’, যৎকিঞ্চিৎ ‘বরবাদ’
আমি ফিল্ম ক্রিটিক বা রিভিউয়ার নই।
ফিল্ম এক মাল্টিডিসিপ্লিনারি আর্ট যাকে দেখি কমার্শিয়াল এবং সোশিওপলিটিক্যাল লেন্সে। একটা ফিল্ম নিয়ে যখন লিখি তার আগাপাশতলা অন্বেষণ করি, অনেকটা মেশিনে আখ মাড়িয়ে রস তৈরির প্রক্রিয়া।

তাই স্পয়লার সংক্রান্ত রিজার্ভেশন থাকলে লেখার বাকি অনুচ্ছেদগুলো না পড়ার কঠোর অনুরোধ রইলো।
দর্শক যখন একই ফিল্মস্টারের একাধিক কাজ দেখে, এবং কোনো একটিতে বড় সাফল্য আসে, দর্শকের শ্রেণি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যা ই হোক, সে ওই ফিল্মস্টারের অপরাপর কাজগুলোকে নির্মোহ মূল্যায়নের সামর্থ্যলুপ্ত হয়। তার ভাবনায় ঘুরতে থাকে অন্য কাজগুলো ওই নির্দিষ্ট ফিল্মটার সাপেক্ষে কতখানি আগানো বা পিছানো৷
মাসালা ফিল্ম ক্যাটেগরিতে ‘তুফান’ শাকিব খানের সেই পিক পয়েন্ট, আগামী ৪-৫ বছরে নানা উছিলাতেই ফিরে আসবে ‘তুফান’ ।
২০০৯ এ রিলিজ পায় তেলুগু ফিল্ম ‘মাগাধিরা’, তেলুগু ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো ফিল্ম ১০০ কোটি ক্লাবে প্রবেশ করে৷ ২ বছর আগে ১০০ কোটি ক্লাব স্পর্শ করেছিল রজনীকান্তের তামিল ফিল্ম ‘শিবাজি’।
তামিল-তেলুগু ইন্ডাস্ট্রি প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী এবং কমার্শিয়ালি সফল হলেও তাদের কালচারাল সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারত ছাপিয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল, বহির্বিশ্ব এবং বাংলাদেশে বিস্তৃত হওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই ফিল্মকে পায়োনিয়ার বলা যেতে পারে।
কলকাতা এবং বাংলাদেশের ফিল্মে তেলুগু-তামিলের অনুপ্রবেশ অধ্যায়ের শুরু আরো আগে, একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত হয়তবা তা সহনীয় ছিল, কিন্তু উল্লিখিত টাইমলাইনের পর থেকে তা রূপ পেয়েছে আধিপত্যতায়। সাউথ ইন্ডিয়ান কালচারাল কনটেক্সট এবং লাইফস্টাইল কলকাতা বা বাংলাদেশের চাইতে পুরোপুরি আলাদা, তাই সেখানকার গল্প এবং প্রেজেন্টেশনকে যদি লোকাল কনটেক্সট অনুসারে কাস্টমাইজড করা না হয়, মার্কেট ইকোনমিক্সে তা ব্যাকফায়ার করতে বাধ্য।
তেলুগু-তামিল-কন্নড়-মালায়লাম এডাপ্টেশনের বিরোধীতা করছি না, তবে লোকালাইজেশনেরও বিকল্প নেই।
তুফান, বরবাদ, দাগী, জংলি- সাম্প্রতিক কালের ৪ ছবিতে নায়কের যে গেট আপ, লুকিং– বাংলাদেশে এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কোনো পুরুষ কি চোখে পড়ে?
কালচারাল ওরিয়েন্টেশন ফিল্মে আদৌ জরুরী কিনা, সেই আর্গুমেন্ট তোলা যেতে পারে৷ শুটিংয়ের লোকেশন-ক্যামেরা ক্রু-এডিটিং-সেট ডিজাইনার সব তেলুগু-তামিল, আর্টিস্টের বড় অংশ কলকাতার ( দুই বাংলার আর্টিস্টের মধ্যে যখন স্ক্রিনে ক্রস কানেকশন ঘটে, ডায়ালেক্টের ভিন্নতা হেতু সংলাপগুলোতে সিনক্রোনাইজেশন হয় না৷)— তাহলে ক্যারেক্টারের নাম বাংলাদেশি, স্থান ঢাকা রাখবারই বা আবশ্যকতা কী? Bongo প্লাটফরমে প্রচুরসংখ্যক তেলুগু-তামিল ফিল্মের বাংলা ডাবিং পাওয়া যায়৷ দর্শক হলে গিয়ে যখন কালচারাল কনটেক্সটহীন এসব ফিল্ম দেখে, তার মধ্যেও কি বাংলা ডাবিং প্রোডাক্ট দেখবার অনুভূতি হয় অবচেতনেই?
সমাধান কী হতে পারে।
আমার মতে তেলুগু-তামিলের রেসিপিটা গভীরভাবে আত্মস্থ করে সেই অনুসারে বাংলাদেশী ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো সংমিশ্রিত করা।
তেলুগু-তামিলের ফান্ডামেন্টাল কিছু উপকরণ থাকে- স্টোরি এবং ক্যারেক্টার বিল্ড আপ, ডার্ক কমেডি, ব্যাকস্টোরি, টুইস্ট, এন্টিক্লাইম্যাক্স, পাঞ্চিং সংলাপ, সাব-প্লট, সাব-ক্যারেক্টার৷ উপকরণগুলোর চূড়ান্ত বহি:প্রকাশ ঘটে ৩ প্রকারে- একশন, ভায়োলেন্স এবং নাচ-গান৷
সবচাইতে ফালতু লাগা তেলুগু-তামিলেও এই রেসিপির নিখুঁত এক্সিকিউশন লক্ষণীয়৷
আমরা কেবল প্রকারগুলোর অন্ধ অনুসরণ করে গেলাম, কিন্তু উপকরণগুলোতে নজর দিলাম না, কম্পোজিশনটা হচ্ছে হৃৎপিন্ডবিহীন শরীরের মতো।

এবার বরবাদ প্রসঙ্গে আসা যাক৷
হুমায়ূন আহমেদের একটা নাটক মনে পড়লো- ‘গৃহসুখ প্রাইভেট লিমিটেড”; রেডিওতে ইনস্ট্রাকশন শুনে শুনে রান্নার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল, মাঝপথে রেডিও গেল বন্ধ হয়ে, অনেক কসরত করেও সাউন্ড ফেরত এলো না। উত্তেজনার বশে রেডিওটাই আছাড় মারলো।
বরবাদেও কি তাই ঘটলো?
ক্ষমতাবানের বখাটে ছেলে আপন খুশিতে অপকর্ম করছে, বাবা অবসেসিভ স্নেহে তাকে রক্ষা করছে– না আছে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট-স্টোরি বিল্ড-এন্টিক্লাইম্যাক্স, না আছে সিগনেচার কোনো কমেডি৷
হিন্দি এনিম্যাল ৫০০ কোটি রুপি আয়ের পরে প্রোটাগনিস্টকে ভিলিফাই করে ফিল্ম তৈরির প্রবণতা বেড়েছে। একই সাথে অঢেল বিত্তশালী হলে যে কোনো নারীকে সেক্সুয়ালি এট্রাক্ট করা সম্ভব, সেই ন্যারেটিভকেও প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও দৃশ্যমান। এ ধরনের ন্যারেটিভ প্রবলেমেটিক এবং আপত্তিকর।
এ ঘরানার ফিল্ম যখন শত শত কোটি আয় করে ফেলে, ধরে নেয়া যায় কালেক্টিভলি মোরাল জাজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ভেঙ্গে পড়েছে।
ফিল্ম মোরালিটি শিক্ষা দিবে বা সমাজ বদলানোর ইশতেহার হবে, সে অলীক প্রত্যাশা রাখি না। কিন্তু যদি একজন নৃশংস খুনী বা সাইকোপ্যাথকে প্রটাগনিস্টরূপে ফিল্মিং করা হয়, তার ব্যক্তিসত্তার বিল্ড আপ এবং এক্সিকিউশন অবশ্যই দেখতে চাইব। রক্ত, জবাই, কামড়াকামড়ি নির্বিচারে দেখেই গেলাম, কিন্তু তার প্রতি কৌতূহলই বোধ করলাম না, এটা পুরোপুরি ব্যর্থ প্রজেক্ট।
দুয়ের মধ্যকার ফাইন লাইনটা বুঝাই- এনিম্যাল দেখাকালীন ক্যারেক্টারের নৃশংসতার পাশাপাশি তার সামগ্রিক ক্রাইসিস আর কমিটমেন্টগুলোকেও ফিল করতে পারি ডিটেইলিংয়ের নৈপুণ্যে, এরপরে আবিষ্কার করি এই চরিত্রে অভিনয় করেছে রনবীর কাপুর।
কিন্তু বরবাদ বা কিছুক্ষেত্রে তুফান দেখাকালীন কোনো ক্যারেক্টার পাই না, সুস্পষ্টভাবে ফিল হয় সিনেমার নামে মূলত শাকিব খানের নানান লুক আর কার্যক্রমকে ক্যামেরাবন্দী করা হয়েছে।
ফিল্ম শেষে মনে থাকে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যের একটিমাত্র সংলাপ- ‘এই জিল্লু মাল দে’; ভোকাল টোনের কৌশলী মিক্সিংয়ে হলের অভ্যন্তরে অতি সাদামাটা এ সংলাপকেও যুগজয়ী লাগতে থাকে।
মাসালা ফিল্মের পারসপেক্টিভে বরবাদ এবং তুফানকে যদি পাশাপাশি ডেস্কে বসাই,
১. গান: তুফানের গানগুলো অনেক বেশি হলফ্রেন্ডলি ছিল৷ আসছে তুফান, দুষ্টু কোকিল গান দুটো যে সেট আপ এবং সাউন্ডের ইনটেনসিটিতে পরিবেশিত হয়েছে, দর্শকের মাতোয়ারা হতেই হত। বরবাদ এর গানগুলো হেডফোনে শোনার জন্য উপযুক্ত, হল কাঁপানোর পটেনশিয়ালিটি নেই। আইটেম গান হিসেবে ‘লাগে উড়াধুরা’ এসেছে সিনেমার অন্তিম অংশে, এবং গানের পরেও রেখে দেয়া হয়েছিল টুইস্ট। ‘চাঁদ মামা’ আইটেম হিসেবে এসেছে প্রথম ১৫ মিনিটেই। নাচের স্টেপগুলো বিভিন্ন তেলুগু গানের হুবুহু কপি, এবং উড়াধুরায় মিমি চক্রবর্তীর পার্টিসিপেশন যতটা ভাইব্র্যান্ট ছিল, চাঁদ মামায় নুসরাতকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন লেগেছে৷
২. চঞ্চল-যিশু ফ্যাক্টর: কলকাতার যিশু সেনগুপ্ত তেলুগু, হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় বাংলা সিনেমায় উপস্থিতি কমে গেছে। তার কাস্টিং নি:সন্দেহে কমার্শিয়াল সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুতর নিয়ামক হতে পারত। তুফানে চঞ্চল চৌধুরিকে যেরকম কমিকাল এবং চৌকষ ক্যারেক্টার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল, কয়েকটা পাঞ্চিং সংলাপ দেয়া হয়েছিল, যিশুর জন্য বরাদ্দ সিকুয়েন্স মাত্র ৪টা, তাকে এনিম্যাল এর ববি দেউল ধাঁচের ভিলেন বানানোর চেষ্টা ছিল, যে সর্বক্ষণ শুক্রক্ষয়ের নেশায় থাকে। এন্ট্রি সিনে পুলিশ স্টেশনে ম্যাসাকার চালানোর মধ্যেও নারী পুলিশ পেয়ে শুক্রক্ষয়, গার্লফ্রেন্ডের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গালর্ফ্রেন্ড রেখে মায়ের উপর শুক্রক্ষয়। কোনো পাঞ্চিং ডায়লগ নেই, চুমুর এক্সপ্রেসন, এবং স্বল্প সিকুয়েন্সে তাকে যে হাইটের নৃশংস হিসেবে ফ্রেমিং করা হয়েছে, শাকিব খানের সঙ্গে ফেস অফ সিকুয়েন্সটা হতে পারত সবচাইতে আইকনিক। ভিলেন গ্যাংয়ের ১৫ তম সদস্য নায়কের কাছে যেভাবে ধরাশায়ী হয়, যিশুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে যিশুর থেকে কাস্টিং এডভান্টেজ পাওয়া গেল না কিছুই।
৩. রিলেটেবল সাব-প্লট: ৯০ দশকের অন্যতম শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইনের জীবনী সম্বন্ধে যাদের জানাশোনা আছে তারা তুফানকে অনায়াসে কানেক্ট করতে পারবেন। এছাড়া সুইডেন আসলাম, নায়ক সোহেল চৌধুরী হত্যাকান্ড, ডিবির এসি আকরাম, ২০০১ নির্বাচনে জামাত ইসলামের ক্ষমতার অংশ হওয়া, নায়ক জসিমের সেট থেকে তখনকার ব্যাক ডেঞ্চার শাকিব খানকে বের করে দেয়া সহ অসংখ্য উপকরণ ছিল। তুফানের বাবাকে ১৯৭৫ সালে নৃশংসভাবে খুন করা হয়, সেই ট্রমা থেকে সে দানব হয়ে উঠে, সারা দেশ দখল করতে চায়— এই দুটা সংযুক্তি থেকে তুফান ক্যারেক্টারের বৃহত্তর ইন্টারপ্রেটেশন তৈরি করার স্কোপ ছিল। বরবাদে সেসব উপকরণ খুবই সামান্য। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় জজ মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যাকে সবাই নাটক বলে। এখানেও গ্রেনেড হামলায় প্রধানমন্ত্রী সহ অনেকে নিহত হয়, গ্রেফতার হওয়া নিরীহ ব্যক্তির নাম সবুজ মিয়া। বড়লোকের বখটে ছেলের সাথে মুনিয়া এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গ্রুপের এক ব্যক্তিকে চাইলে রিলেট করা যায়৷ কিন্তু বিল্ড আপ এতোই দুর্বল, ৩ মাস পরেই আর কানেক্টযোগ্য থাকবে না।
৪. নায়িকা এনডোর্সমেন্ট: তুফানের গল্পে নায়িকা ছিল অপশনাল৷ নাবিলা এবং মিমির মধ্যকার কনট্রাস্ট থেকে কম্পোজিশনাল বিউটি তৈরি হয়েছিল৷ বরবাদ নায়িকানির্ভর গল্প। আরিয়ান তথা শাকিব চরিত্রের কোনো ভিশন নেই, নেশা-খুন খারাবি-নারীলিপ্সাতেই আটকে ছিল জীবন, বাবার ব্যবসায়ের টাকা লোপাট করে মামা বিদেশে সম্পদ গড়ছে জানা সত্ত্বেও ভ্রুক্ষেপ করেনি। মামাকে খুন করলো, দেশের প্রভাবশালী সব নেতাকে ব্রাশফায়ার করলো, শুধুমাত্র নীতুর কারণে। আবার শুক্রবীর ফারহান তথা যিশু তাকে দেখে বলছে- আমি একে বিয়ে করব, এই মেয়ের জন্য ১ হাজারটা খুন করা যায়। শাকিবের ডায়লগ- টাকা আর ক্ষমতায় যা পাওয়া যায় না সেটাই সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ হয়।
অথচ স্ক্রিনে আমরা নায়িকাকে যথেষ্ট চার্মিং ভাববার মতো রসদ কি পেয়েছি? একটু হাসি, কিছু ফেসিয়াল এক্সপ্রেসন, আর ছোট্ট একটা ব্যাকস্টোরি— এ দিয়ে গল্পের সেন্টার অব টেনশন এবং এটেনশন বানানো যায় না আসলে।
৫. এন্ডিং: celebrity worshipping উপমহাদেশের এবং সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক কালচার। যত প্রাচীন উপকথা লেখা হয়েছে সবগুলোই অর্চনা প্রজেক্ট। ধরা যাক বরবাদের সব কাস্টিং একই রেখে লিড রোলে নেয়া হলো বাপ্পী চৌধুরিকে, এই ফিল্ম কি রিলিজ পেত কোনোদিন? রজনীকান্ত বা আল্লু অর্জুনকে ফাঁসি দেয়া হলো শেষ দৃশ্যে, দর্শক গ্রহণ করবে, নাকি গল্পের গরুকে পানিতে ডুবিয়ে হলেও টুইস্টের মারপ্যাচে তাকে বাঁচিয়ে দেয়া হলে দর্শক হাত তালি দিতে দিতে হল ত্যাগ করবে! হল থেকে এক্সিট নেয়াকালীন অনুভূতিটা ভাইটাল মনে করি। বরবাদ থেকে এক্সিটকালীন অনুভূতির সাথে তুফানেরটা মিলিয়ে নিলেই উত্তর পাওয়া যাবে।
এবং
প্রোটাগনিস্ট: তুফানে শাকিব খান তার ব্যক্তিগত বৃহৎ স্বপ্ন পূরণে ছুটেছে। এ পথে তার নানামুখী ইন্টারেকশন আর প্ল্যান করতে হয়েছে। বরবয়াদের আরিয়ানের ইনকাউন্টারের বড় অংশ ব্যয়িত হয়েছে পিএস জিল্লুরকে নানা অর্ডার দেয়ার মাধ্যমে। দুটো মেজর ইন্টারেকশনের একটাতে সে এক অফিসে হামলা করে এমডির গলায় কুকুরের শিকল পরিয়ে টেনে বাইরে এনেছে, অন্যটায় ক্লাবে হামলা চালিয়ে ক্ষমতাধর এক ব্যক্তির পুত্রের মুখে প্রস্রাব করে দিয়েছে– দুক্ষেত্রেই কারণ অভিন্ন: ইধিকাকে অপমান। যুগ বদলাচ্ছে, এধরনের পজেসিভনেসকে এখন যে কেয়ারিংয়ের বদলে অবসেসিভ ডিজঅর্ডার হিসেবে ট্রিট করা হয়, স্টোরিটেলারদের এসব পলিটিকাল কারেক্টনেসে নজর দেয়ার হয়তবা সময় সমাগত!
নায়ক হিসেবে শাকিব খানের জার্নিটা আদতেই সিনেমাটিক। ময়ূরী বা মুনমুনের সাথে দ্বিতীয় নায়ক হিসেবে আলেকজান্ডার বো, আমিন খানদের সাথে দেখেছি; শাবনুর-পূর্ণিমার সাথে লো প্রোফাইল কাস্টিং হিসেবে সিনেমা করতে দেখেছি, অপু বিশ্বাসের সাথে উদ্ভট হাস্যকর সব সিনেমা (পাংকু জামাই, নাম্বার ওয়ান শাকিব খান) দেখেছি, জয়া আহসানের সেই ট্রলিং সংলাপ ‘মা আ আ রো’ তে ক্রিকেটাররূপে দেখেছি। সেখান থেকে কলকাতায় শিকারী, বাংলাদেশে সত্তা, প্রিয়তমা থেকে তুফান, বরবাদেও দেখলাম।
বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার মতো এত বেশি ট্রান্সফরমেশন আর ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাওয়া নায়ক, ২য় জন নেই৷
তার বর্তমান বয়স সম্ভবত ৪৫-৪৬, তার উচিত স্ক্রিপ্টিংয়ে পারটিসিপেশন আরো বাড়ানো, এবং ফিক্সড সম্মানির বদলে প্রফিট শেয়ারিং মডেলে যাওয়া। তাতে গল্প, ক্যারেক্টার, মেকিং, গান সবকিছুতে তার অথরিটি আরো সুসংহত হবে৷ কারণ তুফান, প্রিয়তমা, বরবাদ বা অনাগত ফিল্মগুলোর পরিচালক বা প্রযোজক কে ম্যাটার করে না, দিনশেষে গণমানুষের কাছে এগুলো ‘শাকিব খানের সিনেমা’ হিসেবেই প্রশংসিত অথবা নিন্দিত হবে।