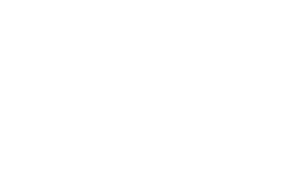সুমিতা দেবীর স্মৃতিকথা/ জীবন নদীর তীরে
[বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি ফার্স্ট লেডি হিসেবে পরিচিতি। সুমিতা দেবীর জীবনকে যেন সিনেমাও হার মানায়। এতটা উত্থান-পতন। কিন্তু কখনো মনোবল হারাননি তিনি। ‘জীবন নদীর তীরে’ স্মৃতিকথায় সে জীবনের কথা বলেছেন। কীভাবে ঢাকাই চলচ্চিত্রের উত্থান, তাও এক টুকরো দলিল এই লেখা। বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ১৯৯১-এ এই স্মৃতিকথা প্রকাশ হয়। সুমিতা দেবী জবানি থেকে অনুলিখন করেন তার ছেলে অনল রায়হান। লেখাটি সুমিতা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অমূল্য দলিল হিসেবে বিএমডিবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো।]

তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তারাপদ লাহিড়ী নামে আমার এক মামাতো ভাই ছিলেন। ভালো হাত দেখতে পারতেন। সে সময় তিনি আমার হাত দেখে বলেছিলেন, ‘হেনা এমন একটা কিছু করবে, যার কারণে অনেক দূর-দূরান্তের মানুষ তাকে চিনবে।’ দূর-দূরান্তের মানুষ আমাকে কতটুকু চিনতে পেরেছে জানি না, তবু অন্তত এ দেশের মানুষ যে আমাকে চেনে, ভালোবাসে-তা তো আমি বিশ্বাস করতে পারি। আমার সেই মামাতো ভাইটি সম্ভবত চলচ্চিত্রের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।
১৯৩৭ সালে পাবনায়, শালঘর গ্রামে আমার জন্ম। সে সময় সন্তান প্রসবের আগে মেয়েদেরকে বাপের বাড়ি চলে আসতে হতো। সে কারণেই মানিকগঞ্জ আমাদের দেশের বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্ম হয়েছিলো পাবনায়। আমার ছেলেবেলা কেটেছে দস্যিপনা করে। শৈশবের অনেক ঘটনার কথাই মনে আছে আমার। প্রতিবছর আমাদের বাসায় দূর্গাপূজা হতো। অষ্টমী পূজার দিন ঠাকুরের জন্য যে ভোগ দেয়া হতো, আমি তা চুরি করে খেতাম। আমার কাছে এরকম লুকিয়ে, গোপনে ঠাকুরের ভোগ খাওয়াটা ছিল দারুণ মজার একটা ব্যাপার। ধলেশ্বরী নদীতে ডুব দিয়ে মাটি তোলা ছিলো আমাদের আর একটা মজার খেলা। একবার এ রকম ডুব-দিয়ে মাটির সঙ্গে একটা কালো পাথর তুলে এনেছিলাম আমি। পাথরটা ছিলো শালগ্রাম শিলা। ভগবান নারায়ণের প্রতীক। বাড়ির সবাই আমার সাথে পাথরটা দেখে আকাশ থেকে পড়েছিলো। বাড়িশুদ্ধ সবাই পাথরটাকে পূজা করতে শুরু করলো। আর বলতে কী একদম হঠাৎ করেই গোটা পরিবারে আমার আদরটাও বেড়ে গেলো দ্বিগুণ।
ছেলেবেলার আরেকটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে আমার। লক্ষ্মীগাই নামে আমাদের একটা গরু ছিলো। লুকিয়ে লুকিয়ে এই গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেতাম আমি। একদিন কী করে যেন এ ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। ব্যস। আমাদের পুরো বাড়িটাকে যেন আতংক গ্রাস করলো। গরুর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেতেন একমাত্র ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। বাড়িসুদ্ধ সবাই ভয়ে হায় হায় করতে শুরু করলো। এ সময় আমার রক্ত আমাশয় হয়। এতে বাড়ির সবার আতংক আরো বেড়ে যায়। ঘটা করে কৃষ্ণ পূজা করা হলো। কিন্তু আমি আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ডাক্তার এসে নিরাশ হয়ে জানিয়ে দিলেন, আমি আর বাঁচবো না। আমাকে ঘর থেকে বের করে তুলসীতলায় নিয়ে আসা হলো। ডাক্তার ঘোষণাই করে দিলেন, আমি মারা গেছি। পরে আমাকে যখন স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হলো তখন নাকি আমি হঠাৎ চোখ মেলে তাকাই।

আসিয়া চলচ্চিত্রের দৃশ্য
আমার বাবার নাম নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বাবারা ছিলেন চার ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের পরিবারের জমিজমা, সম্পত্তি ছিলো প্রচুর। আমি বড় হয়ে উঠেছি এই সম্পত্তি, সমৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই। তবে, রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম হলেও, ছেলেবেলা থেকেই এসব ধর্মীয় অনেককিছুই ভালো লাগতো না। ভেতরে ভেতরে আমি বেড়ে উঠছিলাম অনেকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবনা চিন্তাকে ঘিরে। সে সময়ের একটা ঘটনা আমার মনে দাগ কেটেছিলো ভীষণ। আমার বড় পিসেমশাই ছিলেন ডাক্তার। আমার মনে আছে, তিনি যেদিন মারা যান, সেদিন আমার পিসিমার বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। পিসেমশাই-এর শবযাত্রার সঙ্গে পিসিমা যখন নদী পর্যন্ত যান, তখন তাঁর গায়ে ছিলো রঙীন শাড়ি আর গয়না। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি নদী থেকে ফিরে এলেন, আমি অবাক হয়ে দেখলাম তখন তাঁর গায়ে একটা সাদা কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে তখন বড় উদ্ভট আর বিশ্রী লেগেছিলো।
আমি যখন কলকাতায় পড়ালেখা করছি, তখন আমার বাবা মারা যান। আমরা ছিলাম পাঁচ বোন এক ভাই। এ সময় আমরা একেকজন একেক কাকার কাছে, বা আনন্দ আশ্রমে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে উঠছিলাম। এরকম একটি অবস্থায়, আমার কাকারা হুট করে আমার বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের ঠিক পর পরই আমি জানতে পারলাম, আমার স্বামী অতুল লাহিড়ী কমিউনিস্ট পার্টি করে। সে সময়ে কমিউনিস্টদের ওপর প্রচুর নিগ্রহ হয়েছে। অ্যারেস্ট করা হচ্ছিলো পাইকারীভাবে। অতুল লাহিড়ীর নামেও অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিলো। চুয়ান্ন সালের এই সময়টাতে অতুলকে প্রায়ই পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিলো। এ সময় বেশ কয়েকজন চমৎকার মানুষের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য ঘটে আমার। এরা হলেন কমিউনিস্ট নেতা শান্তি সেন, উপল সেন, মনি সিং, শহীদুল্লাহ কায়সার এবং এদের মতই আরো কয়েকজন। শান্তি দা ছিলেন অদ্ভুত সুন্দর এক মানুষ। গোটা জীবনই তিনি রাজনীতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। শান্তিদা দেখতেও ছিলেন খুব সুন্দর।
এ সময় একদিন ভর দুপুরে এক ভিক্ষুক এসে হাজির হয় আমাদের বাসায়। বরাবরের মত সেদিনও আমি একটু চাল নিয়ে যাই ভিক্ষুকটিকে দেয়ার জন্য। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ অতুল বললো, ‘দাও, আমিই চালটুকু ওকে দিয়ে নিচ্ছি।’ কথাটা বলেই অতুল আমার হাত থেকে চালের পটটা নিয়ে গেলো। অবাক হয়ে আমি দেখলাম, ভিক্ষুকটি আঙুলের হাত থেকে চাল নেয়ার সময় ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো নীচে ফেলে নিলো। অতুল চট করে পা দিয়ে কাগজটা ঢেকে ফেললো। আমি বেশ স্পষ্টই খেয়াল করলাম, ভিক্ষুকটা চলে যাওয়ার পরে অতুল খুব এব আমি জিজ্ঞেস করলাম কাগজটা কিসের, অতুল আমার প্রশ্ন সতর্কতাবে এড়িয়ে গিয়ে বললো, ‘আজ রাতে আমার কিছু অতিথি আসবে তুমি রান্না-বান্না করে রেখো।’ সেদিন মাঝরাতের দিকে শান্তিদাসহ আরো কয়েকজন আমাদের বাসায় এসেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে ওনাদের সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। সেই প্রথম আমি শান্তি সেনকে দেখি। এরকম একটি মানুষকে সারাজীবন শুধু শ্রদ্ধাই করে যেতে ইচ্ছে করে। এই ঘটনার আরো অনেক দিন পরে শাস্তি দার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিলো। মুগ্ধ-বিস্ময়ে আমি খেয়াল করছিলাম, শান্তি দার আদর্শ-নীতি, ভাবনা-চিন্তা সেই আগের মতই আছে। তখনও তিনি লড়াই করে যাচ্ছিলেন, গরীব, মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য। অথচ সময়ের ব্যবধানে অনেক কমিউনিস্টকে আমি দেখেছি, চরম সুবিধাবাদী মানুষে পরিণত হতে।

জহির রায়হানের সঙ্গে সুমিতা দেবী
যা হোক। সেদিন শান্তি দার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলাম আমি। সারারাত তারা কী সব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। একদম কাকভোরে তারা সবাই আবার চলে যান। সেদিন শান্তি দাকে আমি দুপুরবেলার সেই ভিক্ষুকটির কথা বলে জানতে চেয়েছিলাম ঘটনাটা আসলে কি? শান্তি দা তখন আমাকে তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির কথা শোনালেন। তারপর বললেন, ‘এরপর কোনদিন যদি এরকম কোন ভিক্ষুক আসে এবং ফোন কাগজ ফেলে যায়, আমি যেন তা খুব সাবধানে উঠিয়ে এনে অতুলকে দিয়ে দিই।’ বলতে কী, এভাবেই সে সময়ের আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে খুব ক্ষীণতর হলেও একটা যোগসূত্র আমার ঘটে। আমার জীবনে এই অদ্ভুত যোগসূত্রটাকে খুব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমি সব সময়। তাছাড়া, শান্তি সেনের মত নির্ভীক, নিঃস্বার্থ মানুষের সঙ্গে আমি অল্প সময়ের জন্য হলেও মিশতে পেরেছি, একেও আমি আমার জীবনের এক বিরল সৌভাগ্য বলে মনে করি।
সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন সালের দিকে অতুলরা অনেকেই অ্যারেস্ট হয়ে যায়। এরপর অতুলরা যখন ফরিদপুর জেল থেকে ছাড়া পায়, তখন আমার পরিচয় হয় উপল সেন, মনি সিং এবং শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অতুলরা মোট নয়জন আামাদের বাড়িতে আসে। এদের সঙ্গে শান্তি দাও ছিলেন; অবশ্য তিনি তখন অ্যারেস্ট হননি।
এই সব মানুষগুলোকে আমি বার বার দেখতাম। কিন্তু তারপরও আমার কাছে মনে হতো, এরা আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শান্তি দার মত উপল দাও ছিলো তেমনি এক সত্যিকারের মানুষের মত মানুষ। যাদের সাহচর্য আমার ভাবনা-চিন্তাকেও উল্টেপাল্টে দিয়েছিলো।
অতুলের আরেকটা গুণ ছিলো। সে খুব সুন্দর ছবি তুলতে পারতো। ঐ সময়ে প্রায়ই অতুল আমার ছবি তুলতো আর বলতো, ‘তোমার ক্যামেরা ফেস খুব সুন্দর। তুমি ছবিতে অভিনয় করলে ভালো করতে।’ সত্যি বলতে কী, এই ছবি তোলাটা ছিলো আমার চলচ্চিত্রের আসার পেছনে একটা বড় প্রেরণা।
অতুল যখন জেলে ছিলো, তখন কলকাতায় খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো। বিজ্ঞাপনে চিত্ত বসু পরিচালিত ‘রাণী বউ’ ছবির জন্যে নতুন নায়ক, নায়িকা আহ্বান করা হয়েছিলো। বিজ্ঞাপন পড়ে দুই কপি ছবিসহ একটা দরখাস্ত আমি পাঠিয়ে নিই। কিছুদিন পরেই চিত্ত বসুর অফিসে আমার ডাক পড়ে। কিন্তু এ সময়ে দেয়াল হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় আমার পরিবার। আমার মেজমা আমাকে কোনভাবেই যেতে দিলেন না। আসলে, আমাদের মত ওরকম রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের মেয়ে হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবো, তা কল্পনা করাও ছিলেন এক ভীষণ পাপ।
এর আরো কিছুদিন পরে, অতুল যখন জেল থেকে ছাড়া পেলো, সে সময় হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোলো, ঢাকায় নাকি ফিল্ম স্টুডিও হবে এবং ‘পানির সুন্দরী’ নামে একটি ছবি হবে, পরিচালক গোপাল দে সুন্দরম। এই ছবিতে নতুন শিল্পীদের অহ্বান করা হচ্ছে। এ সময় অতুল নিজেই উৎসাহী হয়ে আমার ছবিসহ একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলো। আমাদের গোঁড়া হিন্দু পরিবারে অতুলের এই সিদ্ধান্তটা ছিলো খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ। যা হোক, দরখাস্ত পাঠাবার পর বেশ অনেকদিন চলে গেলো, আমরা কোনো খবর পেলাম না। এ অবস্থায় অতুল আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয় খবর নেয়ার জন্য। ঢাকায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরও গোপাল দে সুন্দরমের কোন খোঁজ পেলাম না আমি। সেবায়ও আমাকে বিফল হয়ে মাদারীপুরে চলে আসতে চলো। এ সময় আমার প্রথম সন্তান হয়। ওর নাম ছিলো স্বপন। যদিও সে বেঁচেছিলো মাত্র এক বছর চারদিন।
এরই মধ্যে অতুল তার এক বন্ধুকে দিয়ে আমার ছবি পাঠিয়ে নিয়ে ছিলো, পরিচালক এ জে কারদারের কাছে। এ জে কারদার তখন ‘জাগো হুয়া সাবেরা’ নামে একটি ছত্রি করছিলেন। এ জে কারদার নাকি আমার ছবি দেখে বলেছিলেন, ‘এ মেয়েটি মোটেই বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালী মেয়েদের নাক এত লম্বা হয় না।’
ভাগ্য আমার সেবারও পিছিয়ে এলো। এ জে কারদার তার ছবির জন্য আমাকে নির্বাচিত করলেও সেবার আমি নিজেই নিজের বাধা হয়ে দাঁড়ালাম। স্বপন তখন মোটে তের-চৌদ্দ দিনের নবজাত শিশু। ওকে মাদারীপুরে ফেলে রেখে ঢাকায় এসে শুটিং করতে আমি রাজী হলাম না।
এরপর শ্রদ্ধেয় লেবু তাই অর্থাৎ ফতেহ লোহানীর ‘লাইফ অব ইস্ট পাকিস্তান’ ছবিতে অভিনয় করার জন্য অতুলের এক বন্ধুর সঙ্গে আমি লেবু ভাইয়ের বাসায় যাই। প্রথম পরিচয়েই লেবু তাইকে আমি শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এই মানুষটি চলচ্চিত্র জীবনে আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। আমার অভিনয়কে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনেক।

কাচের দেয়াল ছবির দৃশ্য
লেবু তাই আমাকে জানালেন, সময়মত তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন। এরই মধ্যে আমার দ্বিতীয় সন্তান মিঠু জন্ম নেয়। মিঠুর বয়স যখন নয়দিন, তখন আমার বড় ছেলে স্বপন মারা যায়। এ সময় আমার মা কলকাতা থেকে মাদারীপুর এলে মিঠুকে মার কাছে রেখে আমি ঢাকা চলে আসি। ঐ সময়টাতে আমার এক রকম জেদই চেপে যায় ছবিতে অভিনয় করার জন্য।
কয়েকদিন পরেই ‘আসিয়া’ ছবির জন্য স্ক্রীন টেস্ট দিতে বি জি প্রেসে যাই। বলতে ভুলে গেছি, এরই মধ্যে ‘লাইফ অব ইস্ট পাকিস্তান’ নাম পাল্টে ছবির নাম রাখা হয়েছিলো ‘আসিয়া’। তখনও আমাদের এখানে এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এফডিসির ল্যাবলেটরীর কাজ সে সময় বি জি প্রেসেই হতো। এই দিনটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমার মনে আছে। সেদিন বি জি প্রেসে প্রজেকশান হল ঘরটায় ঢোকার পরই ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনার সাথে মেকআপের সরঞ্জাম কিছু আছে।’ আমি জানিয়েছিলাম যে সে রকম কোন কিছুই আমার সঙ্গে নেই। তিনি তখন বলেছিলেন, ‘আরে নাজির ভাই তো আপনার দিকে মুখ তুলেও তাকাবেন না।’ যতদূর মনে পড়ে বেবী ইসলাম হাড়াও তখন ঐ ঘরে বসা ছিলেন শ্রদ্ধেয় কলিম শরাফী, লুৎফর রহমান এবং সে সময়ের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মহসীন ভাই। বেবী ইসলাম বলছিলেন, ‘কোত্থেকে যে এই ঝড়ো কাকটাকে ধরে এনেছ্যে। নাজির ভাইতো একে ভালোভাবে দেখবেনও না।’ বলাই বাহুল্য বেবী ভাইয়ের কথায় আমার হন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। আমি যে পারিবারিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিলাম, সেখানে আধুনিক মেকআপ বা ফ্যাশনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিলো না। বরাবরই সাদা-মাটা, একদম সাধারণ বেশভূষায় অত্যন্ত ছিলাম আমি। সুতরাং সেদিক থেকে, বেবী ভাইয়ের কথায় আমি গেঁয়ো বা সেরকম কোন একটা ঝড়ো কাক হলেও হতে পারি।
বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখলাম, বিস্কিট রঙের প্যান্ট, সাদা ফুলহাতা শার্ট আর স্যান্ডেল সু পরিহিত একজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। জানলাম ইনিই ছবির প্রযোজক নাজির আহমেদ। এরপর যথারীতি নাজির ভাই আমার ক্যামেরা-টেস্ট নিতে শুরু করলেন। এক সময় আমাকে হাসাবার জন্য তিনি ক্যামেরায় চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনার দেশ কোথায়?’ ‘মাদারীপুর’। বললাম আমি। এরপর নাজির ভাই ছড়া কাটলেন, ‘চোর-চোট্টাখেজুরী গুড়, সব পাওয়া যায় মাদারীপুর।’ ছড়া শুনে আমিও প্রাণ ভরে হেসেছিলাম। এরপর আসিয়া ছবির স্ক্রীপ্টের একটা অংশও আমাকে দিয়ে পড়ানো হলো। এভাবেই আমার স্ক্রীন টেস্টের পালা চুকলো এবং বেবী ভাইয়ের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী উপেক্ষা করে আসিয়া ছবির নায়িকা চরিত্রের জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হলো। এভাবেই শুরু হলো আমার চলচ্চিত্র জীবনের যাত্রা।
আমিই ছিলাম তখন প্রথম বাঙালী মেয়ে, যে চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করলো। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে এদেশের বাঙালী মুসলমান কিংবা হিন্দু সমাজ ছিলো বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্র চলচ্চিত্রাঙ্গন গড়ে তোলার জন্য সে সময় যারা নিদারুণ আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন, আমাকে পেয়ে স্বভাবতই তারা আনন্দিত হয়েছিলেন।
আসিয়া ছবির শুটিং অল্প কিছুদিন হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আমি ‘আকাশ আর মাটি’ নামের নতুন একটি ছবিতে কাজ করতে শুরু করি। এ ছবিরও পরিচালক ছিলেন ফতেহ লোহানী। এ ছবিতেই প্রথম আমি নায়কের সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয়ের শুটিং করি। এ ছবিতে আমার বিপরীতে ছিলেন কলকাতার নায়ক প্রবীর কুমার।
আটান্ন সালে আমাদের দেশে প্রথম এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। এফডিসি বলতে ছিল, তখন একটা ছোট্ট বিল্ডিং আর একটা মাত্র ফ্লোর। এছাড়া এফডিসির প্রায় পুরো অংশ জুড়ে ছিলো ঘন জঙ্গল। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, সে সময় প্রতি সন্ধ্যায় এফডিসি চত্বরে শেয়াল ডাকতো। এ সময় আমি পালা করে ‘আকাশ আর মাটি’ এবং ‘আসিয়া’র শুটিং করছিলাম।
তখনকার কাজের পরিবেশটাই ছিল আলাদা। ইউনিটের টি-বয় থেকে শুরু করে প্রডিউসার, আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান প্রত্যেকেই কাজ করতো খুব মিলেমিশে। সে সময়ের নাজির ভাইয়ের একটা কথা এখনও আমার মনে পড়ে। তিনি বলতেন, ‘এফডিসি’র বাইরে একজনের সঙ্গে আরেকজনের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, এফডিসির গেটের ভেতর ঢোকার সাথে সাথেই প্রত্যেকেই পরিণত হবে একটা পারিবারে।’ আর সত্যিই, তখন আমরা কাজ করতাম অনেকটা পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই। এমনকি প্রোডাকশনের খাওয়া-দাওয়া হতো সবার জন্য একই রকম। শিল্পী, কলা-কুশলী, ইউনিট বয়, প্রত্যেকেই একই রকম খাওয়া খেতো। কারো জন্য স্পেশাল কিছু করা হতো না কখনও।
তখনকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক বা পরিবেশের কথা, এখন যারা এফডিসিতে কাজ করেন তারা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারবেন না। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। একবার হিন্দুদের দোল উৎসবের দিন আসিয়া’র শুটিং পড়েছিলো। আমাদের ইউনিটে আমি, রনেন কুশারী, মাধুরী চ্যাটার্জিসহ অনেকেই ছিলেন হিন্দু। স্বভাবতই দোল উৎসবের আনন্দ করতে না পারায় আমাদের প্রত্যেকের মন খারাপ হয়েছিলো। ডিরেক্টর লেবু ভাই এলে আমরা তাকে শুটিং প্যাকআপ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আসল ঘটনা জানতে পেরে লেবুভাই উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, ‘কি আশ্চর্য। আজকে যে দোল উৎসব, আমি তো ভুলেই গেসলাম। ঠিক আছে আজকে আমরা হাফ শিফট রং খেলবো আর বাকি হাফ শিফট শুটিং করবো।’ এবারে লেবু ভাই নিজেই প্রোডাকশনের টাকা দিয়ে রঙ কিনে আনালেন। এরপর প্রডিউসার নাজির তাই ফ্লোরে এসে দেখলেন, শুটিং-ফুটিং সব হাওয়া। আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ান সবাই রঙে মাখামাখি হয়ে আছেন। এ সময় আমি নাজির ভাইয়ের পায়ে রং মাখিয়ে দিলাম। হতভম্ব নাজির ভাই যখন পুরো ঘটনা শুনলেন, তখন প্রোডাকশনের টাকার এমন অপচয় দেখেও তিনি মোটেই রেগে গেলেন না বরং তিনিও আমাদের আনন্দে শরিক হলেন। সেদিন আমরা পুরো শিফট জুড়েই হোলি খেললাম-হাফ শিফট শুটিংও আর হয়নি। এফডিসি’র ইতিহাসে ঐ একবারই বোধহয় দোল খেলা হয়েছিলো।
নাজির আহমেদ ছিলেন ঠিক সে ধরনের মানুষ যারা সারাদিন একনাগাড়ে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যেতে পারেন, যাদের সততা, কর্মস্পৃহা অন্যদের ভেতর উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে সময়ে কোন ইউনিট আউটডোরে শুটিং করতে যাওয়ার আগে, নাজির ভাই নিজের হাতে ক্যামেরার লেন্সগুলো রুমাল দিয়ে মুছে দিতেন। এরপর যখন সন্ধ্যায় আউটডোর থেকে ইউনিটে ফিরে এসে এফডিসিতে ক্যামেরা জমা দিত, তখনও নাজির তাই নিজেই ক্যামেরার লেন্সগুলো আবার মুছে রাখতেন। নাজির আহমেদ ছিলেন তখন এফডিসির সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তবু এরকম খুঁটিনাটি অথচ প্রয়োজনীয় কাজগুলোও তিনি নিজের উৎসাহেই করতেন। আজ অবধি ওঁর মত আর কেউ এফডিসিতে এসেছেন বলে আমার জানা নেই।
এফডিসিতে তখন শুটিং চলছিলো, ‘আসিয়া’, ‘আকাশ আর মাটি’, ‘এ দেশ তোমার আমার’ এবং ‘মাটির পাহাড়’-এর যার মধ্যে তিনটি ছবিতেই আমি নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছিলাম। মাটির পাহাড় ছবিতে অভিনয় করছিলেন সুলতানা ভাবী এবং রওশনারা। ‘এ দেশ তোমার আমার’ ছবির পরিচালক ছিলেন এহতেশাম। এ ছবিতে অভিনয় করতে গিয়েই জহির রায়হানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। জহির ছিল এ ছবিতে এহতেশামের সহকারী। জহিরের কাঁধে তখন সব সময় একটা ঝোলানো ব্যাগ থাকতো, দেখতে বেশ লাগতো। এ সময় জহির আর খান আতা হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে হাজির হয়। ঐদিন আমরা সারাদিন আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

কখনো আসেনি ছবির দৃশ্য
যে সময়ের কথা বলছি তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিলো উত্তপ্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তখন আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছিলো। এরপর আটান্নতে সারা দেশে মার্শাল ল’ জারি করা হয়। এ সময় অতুলের বিরুদ্ধে পুনরায় অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বের হয়। অতুল যত দ্রুত সম্ভব কলকাতা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া অবশ্য আর তেমন কোন উপায়ও ছিল না। কিন্তু অতুল আমাকেও তার সঙ্গে কলকাতা চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করে। আমার তখন তিনটি ছবির কাজ চলছিলো। আমার কলকাতা চলে যাওয়ার অর্থ হলো এই ছবি তিনটির সমূহ ক্ষতি। ছবি তিনটির ক্ষতি করে কলকাতা যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিলো না। স্বাভাবিকতাবেই অতুলের প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। অতুল জানায়, আমি যদি তার সঙ্গে কলকাতা না যাই তাহলে সে আমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবে না। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে লিখে দিয়ে যায় যে, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক শেষ।
অতুল চলে যাওয়ার পর বার বার কলকাতা আমার মা, মেজ কাকা-কাকী আমাকে কলকাতায় চলে আসবার জন্য চিঠি লেখেন। এরপর হঠাৎ একদিন আমার মা কলকাতা থেকে এসে হাজির হলেন এবং কেঁদে কেটে বললেন, আমার মেজো বোন অনু নাকি প্রেম করতে গিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছে। এক্ষুণি ঐ ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়া উচিত। সুতরাং আমাকে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমি কলকাতা গেলাম এবং গিয়েই বুঝলাম, আমার মা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন। আমি টের পেলাম অতুল এবং আমাদের পরিবার দুই পক্ষই কলকাতায় আমাকে জোর করে আটকে রাখার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। বলতে কি অনেকটা লুকিয়েই আমি সে সময় ঢাকায় চলে আসি এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মাস দেড়েক পরেই ইন্ডিয়ান হাইকমিশন থেকে আমাকে জানানো হয়, অতুল লাহিড়ী নাকি তাদের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছে যে, ঢাকার মুসলমানরা আমাকে আটকে রেখেছে। ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের দায়িত্ব এখন আমাকে কিছুদিনের জন্য একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে রাখা, অতঃপর আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেয়া। আমি অবাক হয়ে তাদের আনালাম যে মোটেই মুসলমানরা আমাকে এখানে আটকে রাখেননি-এটা একটা মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অতুল আমাকে ভালোবাসতো, কমিউনিস্ট পাটি করতো। তার মতো একজনের কাছ থেকে এতটা নীচতা আমি আশাও করিনি।
শেষ পর্যন্ত অতুলের সঙ্গে আমি ডিভোর্স করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার জীবনে এটা যত রূঢ় সিদ্ধান্তই হোক না কেন, মূলতঃ অন্য সব কিছুর চাইতে চলচ্চিত্রকেই আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম সবচেয়ে বেশি। ফলে কোনক্রমেই এখানকার চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমার যোগ্যসূত্রটাকে ছিন্ন করে কলকাতা চলে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম না।
যা হোক, আমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এবারে বাধ সাধলো আমার ধর্ম। হিন্দু ধর্মে নাকি এভাবে ডিভোর্স হয় না। ঐ অবস্থায় অতুল লাহিড়ীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের একটিমাত্র উপায়ই তখন খোলা ছিল। আর তা হলো ধর্ম পরিবর্তন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলাম আমি। এটা ঊনষাট সালের কথা। আমার মুসলমান নাম রাখা হলো নিলুফার বেগম।
এ সময়ে ‘এদেশ তোমার আমার’ ছবির শুটিং চলাকালীন সময় জহিরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতে শুরু করে। প্রায়ই তখন আমরা দু’জন-দু’জনের সুখ দুঃখের আলাপ করতাম। সে তার মনের সব কথা আমাকে বলতো। আমিও আমার মনের কথা তাকে বলতে শুরু করলাম। আমাদের বন্ধুত্বটা পরিণত হতে হতে প্রেমের জন্য নিলো এবং আমরা বিয়ে করলাম। তবে, বিয়ের খবরটা আমরা একেবারেই গোপন রাখলাম। এ সময় জহির আমাকে ‘কখনো আসেনি’র গল্প শোনায়। জহিরের যে ছবি করার স্বপ্ন ছিলো প্রবল তা আমি জানতাম। তাছাড়া ‘এদেশ তোমার আমার’-এ সহকারী পরিচালক হিসেবেই জহির যে কাজ করতো, তা প্রায় একজন পূর্ণাঙ্গ পরিচালকেরই কাজ। ছবি পরিচালনার ব্যাপারে জহিরের ভাবনা-চিন্তা যে খুবই অগ্রসর আর উন্নত তা ‘এদেশ তোমার আমার’-এ কাজ করতে গিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সুতরাং আমিও মনে প্রাণে চাইতাম যে জহির এবার নিজেই ছবি পরিচালনা করুক।
সে সময় একটি নতুন ছবি করতে গেলে, এফডিসিতে পঁচিশ হাজার টাকা জমা দিতে হতো। এত টাকা আমাদের কারোরই ছিলো না। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে, নাজির ভাইকে অনুরোধ করে বললাম যে টাকাটা ছবি রিলিজ হওয়ার পর পরই জহির দিয়ে দেবে।
শেষ পর্যন্ত এফডিসি থেকে অনুমতি পাওয়া গেলো। জহির রায়হান তার প্রথম ছবি ‘কখনো আসেনি’র শুটিং শুরু করলো ঊনষাট সালেই। তখনও আমাদের এখানে ডাবিং সিস্টেম চালু হয়নি। আসিয়া, আকাশ আর মাটি, এদেশ তোমার আমার— এ সমস্ত ছবির সাউন্ড সরাসরি টেপ করা হয়েছিলো। ‘কখনো আসেনি’র মধ্যে দিয়ে জহির প্রথম আমাদের এখানে ডাবিং সিস্টেম চালু করলো। আমরাও এই প্রথম লুপ দেখে ঠোঁট মেলাতে শুরু করলাম।
‘কখনো আসেনি’র পর জহির শুরু করে ‘কাচের দেয়াল’ ছবির কাজ। জহির এ ছবির কাহিনী পরিকল্পনা করেছিলো বেশ অদ্ভুতভাবে। একদিন হঠাৎ করেই ঘরের মেঝেতে সে চক দিয়ে একটা বাড়ির ছবি আঁকে। বাড়িটার ভেতরে কয়টা ঘর, ঘরগুলোর কোনটার কোথায় অবস্থান, এসব কিছুই সে মোটামুটি ডিটেইল আঁকে। এরপর এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করেই সে তার ‘কাচের দেয়াল’ এর কাহিনী নির্মাণ করে ফেলে। পঁয়ষট্টি সালে ঢাকায় যে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এই কাচের দেয়াল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নয়টি পুরস্কার লাভ করে। এই ছবিতে অভিনয় করে আমিও শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার পেয়েছিলাম ঐ একই উৎসবে।

জহির তার প্রথম দুটি ছবির মধ্যে দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছিলো অন্য সবার চেয়ে আলাদা অবস্থানে। চলচ্চিত্র পরিচালনায় জহিরের উন্নত ধ্যান ধারণা, আধুনিক নির্মাণ কৌশল কিংবা চলচ্চিত্রের শিল্পমানকে বজায় রাখা, এসব কিছুই অহিরকে দ্রুত নিয়ে যায় একজন উচুমানের চলচ্চিত্রকারের অবস্থানে। তাছাড়া ‘কাচের’ দেয়াল কিংবা ‘কখনো আসেনি’র বিষয়বস্তু, কাহিনী এসব ছিলো প্রচলিত ধারার একদম ব্যতিক্রম একটি প্রয়াস।
ঊনষাট সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অভিনেতা এজাজ, রতন কুমার, নায়িকা নীলো, গায়িকা নূর জাহান এরা সবাই ঢাকায় আসেন একটি স্কুলের জন্য চাঁদা তুলতে। সে সময় এদেরকে আমাদের এখানকার বেশ কয়েকটি ছবি যেমন, আসিয়া, মাটির পাহাড়, এদেশ তোমার আমার এবং কখনো আসেনির অল্প কিছু অংশ দেখানো হয়। কখনো আসেনির যে তিনটা রিল তারা দেখেছিলেন তার মধ্যে আমার ‘আমি যাবো আমি যাবো’ সংলাপটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে ওরা আমার খুব প্রশংসা করে।
এর কিছুদিন পর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রখ্যাত পরিচালক হুমায়ূন মীর্জা ঢাকায় আসেন। তখনকার দিনে তাকে পাকিস্তানের হিচকক বলা হতো। ঢাকা এসেই তিনি ‘কখনো আসেনি’ র আমার সেই, ‘আমি যাবো আমি যাবো’ দৃশ্যটি দেখতে চান। কখনো আসেনির সেই দৃশ্যগুলি দেখে তিনি দারুণ খুশী হয়েছিলেন। তখনই তাঁর একটি ছবিতে আমাকে দিয়ে অভিনয় করাবার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পাকিস্তানে গিয়ে ছবি করার তেমন কোন আগ্রহ আমার ছিলো না। কিন্তু জহির আমাকে হুমায়ূন মীর্জার এই প্রস্তাবে গ্রহণ করতে বলে। সে সময় জহির খুব আন্তরিকই চাইতো, ঢাকার মত লাহোরেও দু’একটি ছবিতে আমি অভিনয় করি। শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন মীর্জার প্রস্তাব আমি রাজী হই এবং লাহোরে যাই শুটিং করতে। এটা ছিলো ষাট সালের কথা। শুটিং শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে হঠাৎ একদিন হুমায়ূন মীর্জা আমাকে চুল কাটতে বললেন। চুল কাটার পক্ষপাতি ছিলাম না আমি একেবারেই। আমার মতের কথা মীর্জা সাহেবকে জানিয়ে দিলাম, আমি চুল কাটবো না। তার চেয়ে বরং আমি ঢাকাতেই ফিরে যাবো। আমার মনে আছে, এরকম ব্যবহারে হুমায়ূন মীর্জা আমার ওপর খুব চটে গিয়েছিলেন। অবশ্য চটারই কথা। এরকম এক অবস্থায় ছবির কাহিনীকার রিয়াজ শাহেদ ‘হাবেলী’র গল্পটাকে একটু ঘুরিয়ে পেচিয়ে নতুন একটি কাহিনী দাঁড় করালেন। অতএব ছবির নাম পাল্টে রাখা হলো ‘ধূপছাঁও।’ হাবেলী’র কাহিনীতে সে সময়কার পাকিস্তানের অন্যতম ব্যস্ত নায়িকা বাহার ছিলেন প্রধান চরিত্রে। আমি ছিলাম মূলতঃ দ্বিতীয় প্রধান চরিত্রে। কিন্তু গল্প পালটে যখন ‘ধূপছাঁও’ করা হলো, তখন দেখা গেলো প্রধান চরিত্র হয়ে গেছে আমার। আর বাহারের চরিত্রটি গিয়ে দাঁড়ালো দ্বিতীয় প্রধান চরিত্রে। এ নিয়ে লাহোর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কারো কারো মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বাহার থাকার পরও পূর্ব বাংলার একটি মেয়ে ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবে— লাহোরের অনেকেই তা মেনে নিতে পারেননি।
শুটিং শুরু হওয়ার আগে সকাল-বিকাল টানা দু’দিন আমাকে নাচের রিহার্সেল করতে হলো। ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিলো একটা নাচের দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। শুটিংয়ের দিন সেটে গিয়ে দেখি লাহোর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু লোক এসে জড় হয়েছে ঢাকা থেকে আসা নায়িকার অভিনয় দেখার জন্য। প্রসঙ্গতঃ বাঙালী অভিনেত্রীদের মধ্যে আমিই প্রথম পাকিস্তানী ছবিতে কাজ করি।
সেটে এত সব মানুষের মনোযোগের কারণ হয়ে ওঠাতে আমার তখন কিছুটা লাগছিলো। হুমায়ুন মীর্জা আমাকে বললেন, ‘আপ দোপাট্টা ঠিক করকে আইয়ে।’ আমি কিন্তু কোনভাবেই দোপাট্টা ঠিক করে নিতে পারছিলাম না। পরে বাহার এসে মীর্জা সাহেবের কথা মত আমার দোপাট্টা ঠিক করে দিলেন। কিন্তু নাচের শুটিং শুরু হওয়ার আগে হুমায়ূন মীর্জা আমাকে দিয়ে ছোট্ট একটা দৃশ্য করিয়ে নিলেন। এটা ছিলো একটা সেন্টিমেন্টাল দৃশ্য। এ দৃশ্যে আমাকে কাঁদতে কাঁদতে সংলাপ বলতে হবে। মেকআপম্যান এগিয়ে এলেন আমার চোখে গ্লিসারিন দেয়ার অন্য। ঢাকাতে তখনও আমরা কান্নার দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য গ্লিসারিন ব্যবহার করতাম না। মীর্জা সাহেবকে জানালাম, আমার গ্লিসারিনের প্রয়োজন নেই। এ সময় ক্যামেরাম্যান মাসুদুর রহমান বললেন, ‘সুমিতাদি ডায়ালগ বোলনে কাওয়াক্ত আপ কি আখো মে পানি আনা চাহিয়ে।’ আমি বললাম, ‘চরিত্রটি যদি আমি ঠিকমত বুঝতে পারি তাহলে এমনিতেই আমার চোখে পানি চলে আসবে।’
এরপর দৃশ্যটি টেক হলো। আমিও কাঁদতে কাঁদতে সংলাপ বলে গেলাম। পরে শুনেছি সে সময় উপস্থিত লাহোর ইন্ডাস্ট্রির শিল্পী, কলা-কুশলীরা প্রত্যেকেই নাকি আমার অভিনয় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। আসলে তাদের পক্ষে এটা তাবা অসম্ভব ছিলো যে, গ্লিসারিন ছাড়াও কান্নার অভিনয় করা সম্ভব, উপরন্তু সে অভিনয়টা হয় আরো প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক।

দীলিপ কুমারের সঙ্গে এফডিসিতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুমিতা দেবী
এ ছবিতে কাজ করতে করতেই আরো দুটো ছবির অফার পাই আমি। লাহোরে থাকাকালীন সময় জহিরের সঙ্গে আমার নিয়মিত চিঠি দেয়া নেয়া হতো। জহির আমাকে লিখেছিলো, নতুন কোন ছবির অফার পেলে আমি যেন তার গ্রহণ করি। লাহোরের অচেনা পরিবেশে কাজ করতে আমার ভালো লাগছিলো না। নতুন ছবির অফার প্রত্যাখ্যান করে আমি ঢাকায় ফিরে আসি।
প্রখ্যাত গায়িকা নূরজাহানের সঙ্গে লাহোরে থাকাকালীন সময়ে আমার সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো। সামনাসামনি বসে তাঁর গানও শুনেছিলাম আমি। তিনি ছিলেন আমার খুব প্রিয় একজন শিল্পী। সাবিহা, সন্তোষ এসব শিল্পীদেরও ভক্ত ছিলাম আমি। লাহোরে শুটিং করতে গিয়ে এদের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটে। লাহোরে শুটিং করতে গিয়ে এটা ছিলো একটা বড় পাওয়া।
‘ধুপছাঁও’ ছবিটির শুটিং এর জন্য তিনবার আমাকে লাহোরে যেতে হয়। একষট্টি সালে ছবিটি মুক্তি পায়। এটাই ছিলো আমার প্রথম এবং শেষ পাকিস্তানী ছবি।
লাহোর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লেগেছিলো। ওদের ওখানে শিল্পীদের খুব মর্যাদা দেয়া হতো, আমাদের এখানে এই রীতিটি তেমনভাবে অনুশীলন হয়নি কখনও। বরং যত দিন গেছে, এ বিষয়টি উল্টো গিয়ে শিল্পীদের মান মর্যাদার বিষয়টিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বেশি। শিল্পীদের যে কোন মান মর্যাদা থাকতে পারে, এখন একটা হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হুমায়ূন মীর্জা সে সময় আমাকে বলেছিলেন, ‘তোমাকে দিয়ে যদি একটি চঞ্চল, দেহাতী মেয়ের চরিত্র করানো যায় তাহলে দারুণ হবে।’
ঢাকায় এসে জহিরকে আমি মীর্জা সাহেবের এই মন্তব্যের কথা বলেছিলাম। সম্ভবতঃ জহিরও মীর্জা সাহেবের মতো একই ধারণা পোষণ করতো। কেননা, প্রায় ঐ সময়টাতেই, জহির নির্মাণ করলো ‘সঙ্গম’ ছবিটি। এ ছবিতে আমার চরিত্রটি ছিলো, একটি চঞ্চল, দেহাতী মেয়ের চরিত্র। ‘সঙ্গম’ ছিলো পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি।
এরই মধ্যে আমার আর জহিরের বিয়ের খবর জানাজানি হয়ে যায়। জহিরদের কায়েতটুলীর বাসায় আমি যেতাম অনেক আগে থেকেই। ওদের পরিবারের প্রত্যেকেই আমাকে আপন করে নিয়েছিলো শুরু থেকেই। আমার আর জহিরের বিয়ে খবর শুনে জহিরের মা অবশ্য কষ্ট পেয়েছিলেন। শুরুতে এ বিয়ে তিনি মেনেও নিতে চাননি। পরে অবশ্য তিনি আমাকে গ্রহণ করে নেন। এদিকে আমার পরিবারের দিক থেকেও তেমন কোন সাড়া ছিলো না। তাছাড়া ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়াতে এমনিতেই আমার ওপর পরিবারের সবার যোগাযোগ কমে গিয়েছিলো। ফলে জহিরের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা হিসেবে উপস্থিত হয়নি কখনও।
সে সময় আমাদের জীবনটা কাটছিলো খুব চমৎকার। জহির এবং আমি আমরা দু’জনই দু’জনকে খুব ভালোবাসতাম এবং একে অন্যকে যতটুকু সম্ভব নানা বিষয়ে সাহায্য করতাম।
জহির ছিলো এমনিতে অসম্ভব খেয়ালী আর কিছুটা অলস প্রকৃতির মানুষ। মাঝে মাঝে সে একনাগাড়ে তিন চারদিন ঘরে বসে থাকতো। এরপর হঠাৎ একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতো, তারপর বেরিয়ে যেত। আসলে এ সময়টাতে জহির দিনের পর দিন হয়তো কোন একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতো। তারপর তার চিন্তাটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগতো।
আমার শ্বশুর ছিলেন একজন আলেম মানুষ। তাঁর কথা মতই সে সময় আমি নামাজ পড়াসহ ইসলাম ধর্মের অন্যান্য আনুষঙ্গিক রীতিনীতি শিখতে শুরু করি। সে সময় ‘আকাশ আর মাটি’ এবং ‘এদেশ তোমার আমার’ ছবি দু’টোর প্রচারপত্র পড়েছিলো রাস্তায়। আমাদের কায়েতটুন্সীর বাসার সামনেও ছবি দুটোর পোস্টার লাগানো ছিলো। এ সময় নতুন আরেকটি ছবির পোস্টার পড়ে রাস্তায়। ঠিক সে সময়ে একদিন একটা ঘটনা ঘটে। যার কারণে আমি কিছুদিনের জন্য চলচ্চিত্র থেকে সরে আসি। একদিন আমার শ্বশুর মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে এসে বলছিলেন, ‘আজকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, বৌমার নতুন
আরেকটা নতুন ছবি লাগিয়েছে। আগের ছবি দুটোর চেয়ে এ ছবিটাতে বৌমাকে অন্য রকম লাগছে। তোরা গিয়ে দেখে আয় না।’ দেরীতে হলেও আমি বুঝতে পারলাম আসলে আমার ধর্মভীরু শ্বশুর চান না আমি ছবিতে অভিনয় করি।
তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আর ছবি করবো না এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি অভিনয় ছেড়ে দিলাম। তখন ‘সঙ্গম’ মুক্তি পেয়েছে গোটা পাকিস্তান জুড়ে। পাকিস্তানের প্রথম রঙ্গিন ছবি। অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিলো এ ছবি। আমার অভিনয়ও প্রশংসিত হলো। তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো— আর ছবি করবো না। চলচ্চিত্র অভিনয় ছেড়ে দেয়ার পর আমার অনুভূতি কী হয়েছিলো তা এখন আর বলে কোন লাভ নেই। কেননা চলচ্চিত্রকে আমি ভালোবাসতাম সবচেয়ে আপনভাবে। সে সময়ে এই মাধ্যমটিই আমার ধ্যান জ্ঞানে পরিণত হয়েছিলো। আমার কাছে মনে হয়েছিলো, এটা ছাড়া আমি চলতে পারি না এর কোনভাবেই। কিন্তু তারপরও, জহিরের সঙ্গে সংসার পাতবার পর, ঐ সংসারকে এর কেন্দ্র করেই নিজের তাবৎ সুখ দুঃখকে ভাগ নিতে চাইলাম আমি। সুতরাং শ্বশুরের মন রাখার জন্য এক কথাতেই আমি চলচ্চিত্র জীবন থেকে সরে আসি।
এর কিছুদিন পরেই জহির নতুন আরেকটি ছবি কাজ শুরু করে। এই ছবিটির নাম ‘বাহানা।’ সে সময় জহিরের প্রথম সন্তান বিপুল আমার পেটে। সুতরাং কোনক্রমেই বাহানাতে আমি অভিনয় করতে পাচ্ছিলাম না। জহির কিন্তু নাছোড় বান্দার মতই বললো, আমাকে ছাড়া আর কোন নায়িকাকে সে নেবে না। সে বললো, ‘তুমি যতদিন নায়িকার রোলে অভিনয় করতে পারবে, ততদিনই শুধু আমি ছবি ডিরেকশন দেবো।’

সত্যিই সেই দিনগুলো ছিলো আমার জীবনের এক চমৎকার সুখময় সময়। এই সুখের সময়টা আমার জীবনে ছিলো খুবই ক্ষণস্থায়ী।
শেষ পর্যন্ত ‘বাহানা’ ছবির জন্য কবরীকে কাস্ট করা হলো। বলতে কি, তখন থেকেই আমার আর জহিরের যে চমৎকার সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিলো, তাতে চিড় ধরতে শুরু করে, যা এর পরে আর কোনদিন জোড়া লাগেনি।
বাহানা ছবির শুটিং-এর জন্য সে সময় আমাদের একবার করাচী যেতে হয়। তখন আমার কোল জুড়ে এসেছে আমার তৃতীয় সন্তান বিপুল।
চলচ্চিত্র থেকে তখন আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। বলতে কি, নায়িকা জীবনের একদম ‘টপ’ অবস্থায় থাকাকালীন সময়েই আমি অভিনয় ছেড়ে দিই। কখনও আবার অভিনয় করবো, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, অভিনয়কে একদম সরাসরি পেশা হিসেবে নেবো তা আমি তখন ভাবতেও পারিনি।
যাক সে কথা। করাচী থেকে ফিরে আসার পর জহির এবং কবরীর সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে উঠলো। জহিরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরকম এক সময়ে ‘বাহানা’ রিলিজ হওয়ার আগেই আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ি কায়েতটুলী থেকে চলে যেতে হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার বাহানা নির্মাণের মধ্য দিয়েও এ দেশে চলচ্চিত্রে জহির আরও একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলো। বাহানা ছিলো পাকিস্তানের প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি।
যে কথা বলছিলাম। জহির একদিন আমাকে এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে অন্য কোথাও একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে বলে। বললো, সেও নাকি কিছুদিন পর আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে নতুন বাসায় উঠে আসবে। আমি প্রথমে রাজী হচ্ছিলাম না দেখে সে বিরক্ত হয়ে জানায় যদি আমি অন্য কোথাও বাসা ভাড়া না করি তাহলে সে কবরীকে বিয়ে করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত আমি তাই করলাম। জহিরের কথা মত, কায়েতটুলীর আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা বাসা ভাড়া করলাম দিলু রোডে। জহির আমাকে বারণ করেছিলো, বাড়ির লোকরা যেন আমার চলে যাওয়ার মূল কারণটা জানতে না পারে। ফলে, আমার শ্বশুর বাড়ির প্রত্যেকেই ধারণা করেছিলো যে আমি স্বইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।
ঐ সময়টাতে আমাকে নিদারুণ আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। আমি জানতাম জহির আসবে না। সে আসেওনি।– স্বভাবতই আমাকে আবার চলচ্চিত্রে ফিরে আসতে হয়। এ সময় আমি হায়াৎ শফির ‘জনম জনম কি পিয়াসী’ ছবিতে কাজ শুরু করলাম। কবরীর স্বামী চিত্ত চৌধুরী তখন জহিরের নামে কেস করে। তখনকার খবরের কাগজগুলোতে ঢালাওভাবে এ নিয়ে লেখা হয়। এ সময় মানসিকভাবে আমি প্রচন্ড বিপর্যস্ত ছিলাম। ছেলে দুটোর কথা ভেবে নিজেকে আমি যথাসম্ভব সংযত রাখার চেষ্টা করি। আর্থিক কারণে তখন আমি রেডিও, টেলিভিশন, স্টেজ নাটক, এমনকি ভয়েস অব আমেরিকার প্রোগ্রামও করতে শুরু করি। এরও কিছুদিন পর আমি যখন মগবাজারে আমিনা বেগমের বাসায় ঘর ভাড়া নিলাম ঠিক তখন থেকেই মূলতঃ আমি চরিত্রাভিনয়ে কাজ করতে শুরু করি। আপন দুলাল, আলীবাবা, তেরো নং ফেকু ওস্তাগার লেন এ সমস্ত ছবিতে তখন আমি চুক্তিবদ্ধ হই। নায়িকা জীবনের সমাপ্তি ঘটে আমার এভাবেই, অতি দ্রুত। নায়িকা হিসেবে নিজেকে পুরোপুরি বিকশিত করে তোলার আগে চরিত্রাভিনয়ে নেমে গেলাম আমি। সে সময় কেবলমাত্র একটি ছবিতে আ নায়িকা চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হই। ছবিটির নাম ‘কেন’। এ ছবিটি অবশ্য আজ অবনি মুক্তি পায়নি।
ঐ সময়টাতে নতুন করে রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে আমার যোগসূত্র ঘটে। আমিনা আপা আওয়ামী লীগ করতেন। এই সূত্রে আওয়ামী লীগের কর্মীদের এ বাসায় আসা-যাওয়া ছিলো। প্রায়ই সারারাত ধরে তারা পোস্টার লিখতো। কয়েক দিনের মধ্যেই এদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র হয়ে উঠলো আমার ঘরটি। এইসব ছেলেদের মধ্যে শেখ মণিও ছিল। একদিন পুলিশ এসে আমার ঘরও তল্লাশী করে যায়।
আমার সেই দুঃখ, কষ্টের দিনগুলোয় অনেকেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যিকারের বন্ধুর মত। যাদের সান্নিধ্য সে সময় আমার দুঃখ কষ্টকে কিছুটা হলেও লাঘব করতে পেরেছিলো। এদের মধ্যে যাদের কথা আমার মনে পড়ে, তারা হলেন, চিত্রালীর এস এম পারভেজ এবং হাই ভাই, সাংবাদিক আজিজ মিসির, পরিচালক সালাউদ্দিন ভাই, মোহসীন তাই এবং আনোয়ার হোসেন।
ও রকম এক বিপর্যয়ের সময়ে হঠাৎ একদিন জহির এসে হাজির হয় আমার বাসায় এবং আবার একসঙ্গে সংসার করার কথা বলে। শেষ পর্যন্ত ছেষট্টি সালে আমি আবার জহির পুনরায় একসঙ্গে ঘর করতে শুরু করলাম অনেকটা সেই আগের মতই। তখন আমরা থাকতাম মোহাম্মদপুরে ভাড়া বাসায়। ‘বাহানা’ ফ্লপ করার পর জহির বেশ কিছুদিন চুপচাপ বসে ছিলো। পত্রিকায় ওকে নিয়ে অনেক আজে-বাজে লেখাও ওকে দমিয়ে দিয়েছিলো। এ সময় জহির আবার চলচ্চিত্র পরিচালনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। ‘বেহুলা’ ছবির কাজ শুরু করে দেয় সে। কিন্তু সুখ আমার জীবনে সেবারও বেশিদিন থাকতে চাইলো না। বেহুলা করতে গিয়ে সুচন্দার সঙ্গে জহিরের ঘনিষ্ঠতা হলো।
এসব সময়গুলোর স্মৃতি মনে করা আমার জন্য খুবই পীড়াদায়ক। জীবনের ঐসব ঘটনাগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চাই না আমি। এতে যন্ত্রণা লাঘব হয় না বরং বাড়ে। এ সময় আমি নিজেই প্রযোজনার কথা ভাবতে শুরু করি। জহির-কবরীর মেলামেশার দিনগুলোতে ডাঃ সিরাজউদ্দিন নামে এক ভদ্রলোক আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। ইনিও ছিলেন একজন চমৎকার মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গেই যৌথভাবে আমি আমার প্রোডাকশান শুরু করি।
‘আগুন নিয়ে খেলা’ ছিল আমাদের প্রথম প্রযোজনা। এদিকে জহির-সুচন্দার সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হতে শুরু করে। জহিরের কিছু সহকর্মী তাদের এই সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে নানা রকম ইন্ধন জুগিয়েছিলো। সেসব কথা এখন আর উল্লেখ করে কি হবে? চিত্রনির্মাতা হিসেবে অবশ্যই জহির ছিল একজন সত্যিকারের সৎ, কমিটেট পরিচালক। মানুষ হিসেবে ছিলো অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। তার সাথে কাজ করে অনেকেই ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে। এদের অনেকেই এখন স্বনামে প্রতিষ্ঠিত। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব মানুষগুলো জহিরের যে কোন কাজেই সমর্থন দিতো, ওর দুর্বলতাকে প্ররোচিত করতো।

ছেষট্টি সালে আমি এবং ডাঃ সিরাজউদ্দিন আমাদের যৌথ প্রযোজনায় ‘আগুন নিয়ে খেলা’-র কাজ শুরু করি। এ ছবির মূল নায়িকা চরিত্রে আমি সুজাতাকে নির্বাচন করি। কিন্তু এ সময় জহির আমাকে এই চরিত্রের জন্য সুচন্দাকে নিতে বলে। যেহেতু সুচন্দা বেহুলা এবং আনোয়ারা ছবিতে কাজ করছে, সেহেতু ‘আগুন- নিয়ে খেলা’তেও তাকে নিলে-ইউনিটটা একদম নিজেদের ইউনিট হয়ে যায়। এই ছিলো জহিরের যুক্তি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেয়া দরকার মনে করছি।।
‘বেহুলা’, ‘আনোয়ারা’ এবং ‘আগুন নিয়ে খেলা’-তে শিল্পী মোটামুটি একই ছিলো। জহির এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সুচন্দাকে নিতে বলেছিলো। কিন্তু সুচন্দাকে নেয়ার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না মোটেই। কেননা, আমি ছবি নির্মাণ করলে সুজাতাকে নেবো, এটা অনেক আগে থেকেই সিদ্ধান্ত হয়ে ছিলো। ‘দুই দিগন্ত’ ছবিতে কাজ করার সময়ই আমি সুজাতাকে কথা দিয়েছিলাম যে, আমি যদি ছবি করি তাহলে ওকেই আমি নায়িকা চরিত্রে নেবো। তাছাড়া নায়িকা হিসেবে তখন সুজাতার জনপ্রিয়তা সুচন্দার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং কোনভাবেই আমি রাজী হলাম না জহিরের প্রস্তাবে। এতে যে জহির অসন্তুষ্ট হয়েছিলো তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু, তখন এমনিতেই জহির-সুচন্দার বন্ধুত্ব নিয়ে নানা রকম গুজব বা কথা উঠেছে। প্রায়ই কানে আসতো নানা কথা। একবার তো ‘আনোয়ারা’ ছবির শুটিং-এর সময় জহির-সুচন্দার সম্পর্ককে ঘিরে রানী সরকারের সঙ্গে জহিরের তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়ে যায়। সে সময় ইউনিটের প্রত্যেকেই এ বিষয়ে কানাঘুষা করতো। কিন্তু সাহস করে কেউ জহিরের মুখোমুখি হতো না। আনোয়ারা ছবির লোকেশনে জহির এবং সুচন্দা বেশ খোলামেলাই মিশতে শুরু করেছিলো। আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হিসেবে রানী সরকারের কাছে এই মেলামেশাটা ভালো লাগেনি। এটা ছিলো স্বাভাবিক। রানী সরকার অন্য সবার মত চুপ করে থাকেনি। জহিরের কাছে সরাসরি এর প্রতিবাদ করেছে। যার ফলে ‘আনোয়ারা’ ছবির পর জহিরের আর কোন ছবিতে রানী সরকারকে দেখা যায়নি। জহির আর তাকে ডাকেনি। অথচ অভিনেত্রী রানী সরকার সম্পর্কে জহিরের মূল্যায়ন ছিলো অনেক উঁচু। জহিরের মতে রানী সরকার খুব বড় মাপের শিল্পী। জহির নিজেই কয়েকবার বলেছিলো, রানী সরকার যদি এ দেশে না জন্মে উন্নত কোন দেশে জন্মাতো, তাহলে সে নাকি খুব নাম করা আর্টিস্ট হতে পারতো। তা। সেই জহিরই, রানী সরকারকে কোনদিন তার ছবিতে ডাকেনি আর।
আমার প্রযোজনার প্রথম ছবি ‘আগুন নিয়ে খেলা’ রিলিজ হলো সাতষট্টিতে। এরপর আটষট্টিতে কাজ শুরু করলাম দ্বিতীয় ছবি ‘মোমের আলো’র। এরপর একে একে ‘মায়ার সংসার’, ‘আদর্শ ছাপাখানা’ এবং ‘নতুন প্রভাত’ প্রযোজনা করলাম। এ সময়ে জহির বনালো ‘আনোয়ারা।’ তারপর আমার জীবনের আরও একটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের সূচনা হলো। শেষ পর্যন্ত জহির এবং সুচন্দা বিয়ে করল। একই সময়ে আমি জহিরের দ্বিতীয় সন্তান পার্থকে জন্ম দিলাম। ঐ সময়টা ছিলো আমার, জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার সবচেয়ে কঠিন সময়। এ সময়ে মানসিকভাবেও আমি ভেঙ্গে পড়লাম।
এরপর এলো একাত্তর। আমাদের স্বাধীনতা/যুদ্ধ। জুন মাস পর্যন্ত আমি ঢাকাতেই ছিলাম। মার্চে পাকবাহিনী আমাদের পাড়ার আক্রমণ করলে, পাড়ার বেশ কিছু অবাঙ্গালী সেদিন আমাকে রক্ষা করে। এরপর আমি বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসি এফডিসিতে। সাদেকুর রহমান সাহেব ছিলেন তখন এফডিসি’র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ সময় আমি মিতা ফিল্মস-এর ব্যানারে একটা দুটো করে অনেকগুলো এফডিসি’র আইডেন্টি কার্ড বের করেছিলাম। এইসব আইডেন্টি কার্ডগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দিতাম। প্রতিরাতেই এরা তখন এফডিসির ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আত্মগোপন করতো। দিনের বেলা এরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যেত। শহরের আনাচে-কানাচে গেরিলা অ্যাকশান করাই ছিলো এদের কাজ।
এ সময় টেলিভিশন থেকে এদিন আমাকে ডেকে পাঠানো হয় অনুষ্ঠান করার জন্য। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত অনুষ্ঠান ছিলো পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থপ্রণোদিত, আমাদের স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী। ঐ সময় আবদুল্লাহ আল মামুন আমাকে বললেন, ‘দিদি আপনার তো কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন আছে, আপনি চলে যাচ্ছেন না কেন? এখানে থাকলে ওরা আপনাকে দিয়ে জোর করিয়ে অনুষ্ঠান করাবেই।’
যা হোক, তারপর আমি বাচ্চাদের নিয়ে কলকাতা চলে আসি। তখন জুন মাস। সে সময় বাংলাদেশে পুরোদস্তুর যুদ্ধ চলছিলো। এরই মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রায়ই অনুষ্ঠান করতাম আমরা।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমরা অনুষ্ঠান করতাম প্রায়ই। যাদের কথা আমার মনে পড়ে, তারা হলেন, হাসান ইমাম, উদয়ন চৌধুরী, রাজু আহমেদ, নারায়ণ ঘোষ মিতা, সুভাষ দত্ত, অমিতা বসু, এরকম আরো অনেকে। আমি মনে করি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সে সময় অনেক প্রতিভাদীপ্ত সংগীত ও নাট্যশিল্পীর জন্ম দিয়েছে। এরই মধ্যে জহির রায়হানকে সভাপতি করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পী কুশলীরা ‘বাংলাদেশ ফিল্ম আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানস এসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই এসোসিয়েশনের হয়ে আমরা কলকাতাস্থ আমেরিকান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোত প্রদর্শন করি। ঐ সময় প্রায় প্রতিদিনই জহিরের সাথে আমার দেখা হত। থেকে থেকেই ক্যামেরা নিয়ে সে চলে যেতো বিভিন্ন ফ্রন্টে। মুক্তিযুদ্ধের কঠিন-করুণ চিত্রগুলো জহির তুলে রাখার চেষ্টা করেছিলো সেলুলয়েডে। সে সময়ের জহির পরিণত হয়েছিল একজন আশ্চর্য পরিপূর্ণ মানুষে। তার সে সময়কার কর্মতৎপরতা এখনও আমার চোখে ভাসে উজ্জ্বল হয়ে। এ সময় আমরাও কলকাতা, বোম্বে, কানপুর এসব জায়গায় নাটক, ভ্যারাইটি শো ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে গেছি স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত। এসব অনুষ্ঠান থেকে আয়কৃত অর্থের শতকরা ষাট ভাগ আমরা জমা দিতাম মুক্তিযুদ্ধের ফান্ডে, বাকী চল্লিশ তাগ আমরা নিজেরা ভাগ করে নিতাম। ঐ সময়ে অনেক শিল্পীরই কলকাতার প্রবাস জীবনে, টিকে থাকার কোন অবলম্বন ছিল না। এই টাকা এইসব শিল্পীদের জন্য যথেষ্ট উপকার করেছিলো। যুদ্ধ চলাকালীন সময় ইন্ডিয়ায় আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়েছিলেন, তা আমরা অনেকেই কম বেশি দেখেছি বা জানি। জহির এইসব ভন্ডামীর অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছিলো। যার মাশুল দিতে গিয়ে তাকে স্বাধীনতার দেড় মাসের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যেতে হয়।
স্বাধীনতার পর থেকে, ক্রমেই আমার জীবনটা হয়ে উঠেছে দুঃসহ। একাত্তরের পর কয়েকটি বছর কোনরকমে কেটেছিলো। কিন্তু তারপর থেকে আমি যেন ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। এখন তো, নিজেকে নিঃশেষিত মনে হয়।
জহির নিখোঁজ হয়ে যায় বাহাত্তরের ৩০ জানুয়ারী। ঐদিন ছিলো, ‘বাংলাদেশ আর্টিস্ট এন্ড টেকনিশিয়ান এসোসিয়েশন’ এর মিটিং। জহির ছিলো এই সংগঠনের সভাপতি। রমনা পার্কে এই মিটিং হওয়ার কথা ছিলো বিকেল ৩টায়। মিটিং এ একে একে আমরা সবাই এলাম। কিন্তু জহির তখনও অনুপস্থিত। এ সময় আলমগীর কবীর এলেন। তিনি জানালেন যে, জহির সেই যে মিরপুর গেছে এখনও ফেরেনি। আমাদের মিটিং আমরা সেখানেই বন্ধ রাখলাম। আমি চলে এলাম রেডিওতে। ইতিমধ্যে জহিরের নিখোঁজ সংবাদটা ছড়াতে শুরু করেছে। রেডিও থেকে বেরিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম, জহিরকে সকালে রফিকুল ইসলাম নামে এক ভদ্রলোক যিনি আমেরিকান কালচারাল সেন্টারে কাজ করতেন,– টেলিফোন করে জহিরের মেজ বোন বেবীকে বলেন, আপনার বড়দা শহীদুল্লাহ কায়সারকে পাওয়া গেছে। এক্ষুণি জহিরকে টেলিফোন দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জহিরকে ফোন দেয়া হয়। জহিরের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথা হয় ঐ ভদ্রলোকের। তারপরই জহির বেরিয়ে যায় মিরপুরের উদ্দেশ্যে।
বড়দাকে জহির ভালোবাসতো তার মায়ের চেয়েও বেশি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জহির ফিরে এসে বড়দার সংবাদ শোনার পর ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছিলো। এ সময় সে একবার আজমীর শরীফ পর্যন্ত গিয়েছিলো— বড়দার নিখোঁজ সংবাদ পাওয়ার আশার। রহস্যজনক সেই টেলিফোন পাওয়ার পর জহির আর কোন যুক্তিতর্ক বাছবিচারে যায়নি। সঙ্গে সঙ্গেই মিরপুর চলে যায় সে। তারপর। আর ফিরে আসেনি।
অনেকেই বলে জহিরকে নাকি পাকিস্তানীরা মেরে ফেলেছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশার সাথে এই হত্যা রহস্য নাকি জড়িত। আমি তা মনে করি না। হ্যাঁ। সে সময় জহির ঢাকায় থাকলে বড়দার মত পাকিস্তানীরা অবশ্যই তাকে ধরে নিয়ে যেত। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় দেড় মাস পরে যখন গোটা দেশ জুড়ে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান, ঠিক সে রকম একটি সময়ে জহিরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটাকে যারা অতটা নিরামিষ যুক্তি দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন (পাকিস্তানীরাই মেরে ফেলেছে), তারা আসলে এই রহস্যটাকে আরো সুন্দরভাবে চাপা দেয়ারই একটা প্রয়াস পান। একাত্তরের যুদ্ধ চলাকালীন জহির অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছিলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় এসে প্রেস ক্লাবে সে বলেও ছিলো যে, এইসব তথ্য রহস্য, সে প্রকাশ করবে। এদেশের কেউ কি একবারও ভাববার মত অবকাশ পাননি যে জহির রায়হানের সংগৃহীত সেই সব তথ্যগুলি কি? সেই তথ্যগুলি বা স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় সংগৃহীত সেই সব দলিলচিত্রগুলি এখন কোথায়? জহিরের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সাথে এই সব তথ্যের সম্পর্ক কোথায়? এরকম হাজারটা প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি এখনও। আসলে, সত্যি কথাটা যত অপ্রিয়ই শোনাক, তবুও বলছি, জহির রায়হানকে এদেশ ভুলতে বসেছে। যেমনি ভুলে যাচ্ছে একাত্তরের রাজাকার আল বদরদের সেই নৃশংসতা। এভাবেই বোধহয় একদিন ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায়।
জীবনটাই ছিল আমার নানা উত্থান-পতন আর ভাঙ্গা-গড়ার। আধুনিক রাজনৈতিক চেতনা, দর্শনের সঙ্গে যেমন আমার পরিচয় ঘটেছে, যোগসূত্র ঘটেছে গোপন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে, তেমনি জীবনের এই শেষ তাগে এসে হঠাৎ করেই অদৃষ্টবাদী ধ্যান ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি আমি। ছিয়াত্তর-সাতাত্তর সালের কথা। চলচ্চিত্র থেকে তখন আমি এক রকম নির্বাসিত। টিভি কিংবা রেডিও থেকে যে আয় হচ্ছিলো তাতে আমি কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না কোনভাবেই। চারপাশ থেকে হতাশাই যেন আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিলো ক্রমশঃ। কোথাও এতটুকু সান্ত্বনা পাওয়ার কোন পথ আমার ছিলো না। ঠিক এমনি একটি সময় চিটাগাংয়ে মাইজভান্ডার শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আমার। এ সময়ের ক্যামেরাম্যান মাহফুজ, নৃত্য পরিচালক বাবু— এরা ছিলো মাইজভান্ডারের মুরিদ। বলতে কি তাদের মাধ্যমেই মাইজভান্ডার শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আমার এবং আমি মুরিদ হই। এরপর যতদিন গেছে, মাইজভান্ডারের প্রতি আমার অনুরাগ, বিশ্বাস, আস্থাও বেড়েছে অনেক। আসলে ক্রমাগত যে হতাশা-নিরাশার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছিলাম আমি, সেই ভয়ংকর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার একটি আপাতঃ পথ হিসেবেই মাইজভান্ডার শরীফকে বেছে নিয়েছিলাম আমি। এখনও মন যখন অশান্ত হয়, এখানে আমি শান্তি খুঁজে পাই। মাইজভান্ডারে আমার যে সব পীর ভাই বোন আছে, তারা অনেক সময় আমাকে সহায়তা করেছেন; আমার মানসিক যন্ত্রণার ভাগীদার হতে চেয়েছেন। আমার দুঃসময়ে তাদের এই ভালোবাসা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া বৈকি।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই আমাকে আমার মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হয়। এরপর বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে। অতঃপর তারা আমাকে রীতিমত উচ্ছেদই করে। এ সময় কয়েকদিন আমি আমার সন্তানদের নিয়ে আমার বাসার গ্যারেজ ঘরে ছিলাম। এ ঘরটা ছিলো মূলতঃ মিটার ঘর। সারা বাড়ির ইলেকট্রিক সুইচ, মেইন সুইচ ইত্যাদি এ ঘরের এক অংশে জায়গা করে নিয়েছিলো। ব্যস। ঐ ঘরটাকেই তখন আমি আমাদের থাকার জায়গা করে নিলাম। এ ঘরটা ছিল বাড়ির বাইরের অংশে। ঐসব সিনগুলোয় আমি আমার ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি,– জীবনটা এত বেরসিক হয়ে যাচ্ছে কেন? এই দেশ, এ দেশের চলচ্চিত্র, এসব কিছুর জন্য ছিটেফোঁটা হলেও কিছুই কি করিনি আমি?
অবাক হয়ে ভাবতাম, বিপুল, পার্থ ওরাতো জহিরেরই সন্তান? সে আজ নেই। শহীদুল্লাহ কায়সারও নেই। এইসব মানুষ যারা এদেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেলো। যাদের সাহিত্য, চলচ্চিত্র কিংবা সাংবাদিকতার কর্ম এদেশের এক অমূল্য সম্পদ,– সেই তাদের সন্তান হয়ে বিপুল, পার্থর জীবন এত অনিশ্চয়তার মধ্যে এত যন্ত্রণার মধ্যে বেড়ে উঠবে কেন? এরকম এক অর্থহীন স্বাধীনতাই কি এনেছি আমরা?
এরশাদ সরকারের আমলে তৃতীয়বারের মত আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এরশাদ সরকারতো সরাসরি জানিয়েই দেয়–জহির রায়হান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ নন। সুতরাং শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার পরিবারের কোন পূনর্বাসন সরকার করবে না। সুতরাং….। এ সময় যেদিন আমার বাসায় উচ্ছেদ অভিযান হয় সেদিন আমার বিপুলের ম্যাটিক পরীক্ষা ছিলো। পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে সে দেখে যায় তাদের বাড়ির মালপত্র সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দেয়া হচ্ছে। এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় কালেজগেটস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা সদলবলে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের প্রতিরোধের মুখে পুলিশসহ সরকারী লোকজন চলে যেতে বাধ্য হয়। এই সব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আমি আজন্ম ঋণি। সত্যিই এক চমৎকার ভাগ্য নিয়ে বিপুলরা এসেছিলো এই পৃথিবীতে, না পেয়েছে নিজের বাবার সান্নিধ্য, না পেলো তার বাবার দেশপ্রেমের প্রতিদান।
যাক সে কথা। এখনও আমি ঠিক এমনি এক অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাস অপেক্ষা করছি কবে আবার চতুর্থবারের মত জহির রায়হানের সন্তানদের রাস্তায় নামতে হবে, পরবর্তী উচ্ছেদ অভিযানের শিকার হয়ে। এটা আমার জন্য প্রায় এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়েই দাঁড়িয়েছে।
তবুও আমি থমকে দাঁড়াইনি কখনও। গোটা জীবনের মতই এখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছি আমি জীবনের সঙ্গে। আমি জানি, আমার সন্তানদের আমি কত কষ্ট, কত যন্ত্রণার মধ্যে বড় করে তুলেছি। ওদেরকে কখনও বুঝতে দিইনি, আর্থিক অভাব অনিশ্চয়তার কথা। যেভাবে পেরেছি, যখন পেরেছি ওদের স্বাদ আহ্লাদ আমি পুরণ করার চেষ্টা করে গেছি সব সময়।
আমি ওদের বড় করে তুলেছি এমন এক মুক্ত পরিবেশে, যেখানে তারা বিকশিত হয়ে উঠতে পারে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে। আমি চাই, ওরা ওদের বাপ-চাচাদের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করুক। যে কাজ সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখতো একদিন জহির রায়হান কিংবা শহীদুল্লাহ কায়সার, সেই কাজকে সম্পন্ন করুক ওরা। আমি জানি ওরা পারবে।
একইভাবে সুচন্দার ঘরে জহিরের যে দুই ছেলে অপু আর তপু, ওদের সঙ্গেও বিপুল, পার্থর যেন সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে চেষ্টাই করেছি আমি। এখনতো ওরা চার ভাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আমি দেখি। আমার ভালো লাগে। সুচন্দা এই সেদিনও অপু, তপুকে নিয়ে আমার বাসায় এসেছিলো। আমিও বিপুল পার্থকে নিয়ে গিয়েছিলাম সুচন্দার বাসায়। কেউ যদি ভেবে থাকেন জহিরের ছেলেদের মধ্যে ইচ্ছে করলেই সৎভাই সুলভ আচরণকে প্রতাবিত করতে পারবেন, তাহলে তারা মস্ত ভুল করবেন। যা ছিল তা ভেঙে গেছে। যা আছে, তা ভাঙবেনা কোনদিন।
ছেলেদেরকে আমি বড় করে তুলেছি বাধার আদর্শ এবং চেতনায়। শিখিয়েছি বাবাকে শ্রদ্ধা করতে। জহিরের কর্মজীবন সম্পর্কে তাদের বলেছি। জহিরের সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছি। আমি কখনও চাইনি বাবার সম্পর্কে অন্য কারো কাছ থেকে অপ্রিয় কোন কথা শুনে বাবাকে ওরা ভুল বুঝুক। আমার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বিপুল, পার্থ ওদের বাবার জন্য গর্বিত। আমি চাই ওরা যতটুকু সম্ভব একজন বিকশিত মানুষ হয়ে উঠুক। যেমন দেখেছি আমি শান্তি’দার মধ্যে।
এ পর্যন্ত আশি থেকে নব্বইটার মত ছবি করেছি আমি। সঠিক সংখ্যাটি মনে নেই। আমার এই দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবন আমাকে দিয়েছে অনেক, নিয়েছেও অনেক। যে সময় আমি চলচ্চিত্রে আসি, সেটা ছিলো এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনাপর্ব। তারপর থেকে গড়িয়েছে অনেক সময়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প এবং আমি বেড়ে উঠেছি প্রায় এক সঙ্গে হাতে হাত ধরে। দু’জনাই, দু’জনকে ভালোবেসেছি আপনজনের মত। যদিও এই সম্পর্ক প্রায় বিছিন্নতার পর্যায়েই। সে আরো বিকশিত হয়ে উঠবে, কিন্তু আমাকে থেমে যেতে হবে এখানেই। এটাই নিয়ম। তবু, তার যেকোন সমস্যাতেই আমি পাশে এসে দাঁড়াবো বিশ্বস্ত বন্ধুর মত। দাঁড়াবো কেন-দাঁড়িয়েছিও। এই তো উননব্বই-এর কথা। মাত্র দেড় বছর আগে। বিগত সরকারের ক্যাপাসিটি ট্যাক্স আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে গোটা চলচ্চিত্র অঙ্গন হঠাৎ করেই
রাজপথে নেমে আসে। আমিও বসে থাকিনি। সবার সঙ্গে আমিও নেমে এসেছিলাম রাস্তায়। কি আশ্চর্য এই দেশ। চলচ্চিত্র শিল্পীদের মিছিলে পুলিশ আক্রমণ করলো নির্দ্বিধায়। পুলিশের লাঠির বাড়ি পড়লো আমার শরীরে। এমনকি কেউ একজন আমার গায়ে তার জুতো দিয়ে সজোরে লাথিও মারলো। আমার মনে আছে, সে সময় বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলাম আমি। পরে লোকে ধরাধরি করে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে। গোটা দেহে অপমান আর লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে ফিরে আসি আমি। তারপরেও থেমে থাকিনি আমি। প্রেসক্লাবের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য যে অনশন ধর্মঘট শুরু হয়, অবলীলায় তাতে যোগ দিই আমি।
এ দেশের কাছ থেকে অন্য ভালো কিছু আর আশাই বা করি কি করে আমি? যে দেশ জহির, শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনির চৌধুরীদের কথা ভুলে যায় অবলীলায়, যে দেশ একাত্তরের ঘাতকদের ভালোবেসে ঠাঁই দেয় তার বুকে নির্দ্বিধায়,–সেই দেশ মুক্তযুদ্ধের শহীদদের যোগ্য সম্মান দেবে–তা আশা করাই তো বাতুলতা মাত্র। সেদিন পুলিশের জুতো আর লাঠির বাড়ি খেয়ে মনে হয়েছিলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ‘ফাস্ট লেডি’ সুমিতা দেবীর জন্য এটাই উপযুক্ত পুরস্কার। হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি এখন আর আমি আশা করি না। করতে চাইও না।