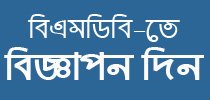পারসপেক্টিভ প্যাকেজ ‘দাগি’
‘দাগি’ এবং ‘বরবাদ’ দুটোই দেখেছি জেনে কেউ যদি অফার করে তার সঙ্গে একটি ফিল্ম পুনরায় দেখতে, আমি নির্দ্বিধায় দাগিকে বেছে নিব
শাহরুখ খানের ‘জাওয়ান’ বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ১১৫০ কোটি রুপি, মোহনলালের ‘দৃশ্যম’ এর আয় ৬২ কোটি রুপি, অজয় দেবগনের হিন্দি সংস্করণ ১০৮ কোটি। একই মানুষ ‘জাওয়ান’ এবং ‘দৃশ্যম’ দেখতে পারে, থিয়েটার এক্সপেরিয়েন্সের দিক থেকে জাওয়ান এক্সাইটমেন্ট দিবে, কিন্তু বছর দশেক পরে ফিল্মের স্মৃতিচারণ করতে গেলে দৃশ্যমই মনে পড়ে বা পড়বে। উইকিমতে, কেরালার হলগুলোতে মোহনলালের দৃশ্যম চলেছে এক নাগাড়ে ১৫০ দিন!দুটোই দেখেছি, তাই স্টেটমেন্টের রেফারেন্স হিসেবে নিজেকেই রাখলাম।

[ডিসক্লেইমার: স্পয়লার সংক্রান্ত রিজার্ভেশন থাকলে আমার ফিল্ম সংক্রান্ত লেখালিখি পড়তে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করছি]
আমি যখন থেকে ফিল্ম দেখি (১৯৯২-৯৩), সেই সময়ের বাংলাদেশী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ক্যারেক্টার ৩টি ধারায় বিভক্ত ছিল।
- এনজিওবাদি ধারা, যারা বিভিন্ন এনজিও এর অনুদানে ফিল্ম তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন করত, ব্যবসার চাইতে এক্টিভিজম হিসেবে দেখা উচিত।
- কাওরানবাজার এবং কাকরাইল ধারা। এরাই নিয়ন্ত্রণ করত এফডিসির ফিল্ম, মিডিয়াতে তাদের উপস্থাপন করা হত ‘মূলধারার কমার্শিয়াল ফিল্ম’ হিসেবে।
- নাটকপাড়া ধারা। এর অন্যতম পথিকৃৎ হুমায়ূন আহমেদ।
হুমায়ূন আহমেদ যখন আগুনের পরশমণি শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারি প্রভৃতি ফিল্মগুলো নির্মাণ করতেন, অধিকাংশ কলাকুশলী থাকতো টেলিভিশন মিডিয়ার, গল্পগুলো বাছাই করা হতো তার কোনো উপন্যাস থেকে৷ এফডিসিকেন্দ্রিক ফিল্মগুলোতে থাকতো মারামারি, ধুম ধারাক্কা নাচ। সংলাপ এবং ডেলিভারি, দুয়ের মধ্যে মাত্রাগত বিশাল পার্থক্য।
এফডিসি গোষ্ঠী এ ধরনের স্টোরিনির্ভর ফিল্মিংয়ের নাম দিয়েছিল- ‘নাটক’, পরবর্তীতে টিভি মিডিয়াতে কাজ করা কোনো পরিচালক ফিল্ম করলেই তাকে টেলিফিল্ম অথবা নাটক বলে আন্ডারমাইনিংয়ের ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যেত, সময়ের প্রবহতায় তা এখন ন্যারেটিভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
করোনা উত্তর পৃথিবীতে এখনকার নতুন বিভাজন- ‘হল ম্যাটেরিয়াল’ বনাম ‘ওটিটি আইটেম’, আমরা একে রিফ্রেজ করতে পারি মোবাইল বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে একা দেখব, নাকি অনেক মানুষের মধ্যে বড় স্ক্রিনে দেখব।
‘দাগি’ কোন প্রান্তিকে পড়ে বুঝবার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রশ্ন করি বড় স্ক্রিনে দেখার সময় কোন কোন এলিমেন্টের প্রত্যাশা থাকে-
প্রথমত, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। ছোটস্ক্রিনে বিজিএম এর ফিল পরিপূর্ণরূপে কখনোই পাওয়া যায় না।
দ্বিতীয়ত, শট ডিভিশন। লং শট এবং ওয়াইড এঙ্গেল শট এর লুক এন্ড ফিল অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। ক্যারেক্টারের সাথে যখন ল্যান্ডস্কেপও প্রাসঙ্গিকতা পায়, এই কম্পোজিশনাল বিউটি ছোট স্ক্রিনে আর সাধারণ সাউন্ডে অনুধাবন অসম্ভব।
তৃতীয়ত, ফেসিয়াল এক্সপ্রেসন। মাইক্রোস্কোপে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসই ধরা পড়ে, বড় স্ক্রিনে ইমোশনের মাত্রাভেদে ফেসিয়াল এক্সপ্রেসনের বহুমাত্রিক তারতম্যগুলো প্রকট হয়ে উঠে।
চতুর্থত, তাৎক্ষণিক এবং স্বত:স্ফূর্ত রেসপন্স। কোনো পাঞ্চিং সংলাপ, কমেডি, একশন, নিষ্ঠুরতা বা রোমান্টিক দৃশ্য, এমনকি একটা সামান্য চাহনিও হতে পারে যা দেখে মুহূর্তে রিএকশন তৈরি হয়। ছোট স্ক্রিনে একাকী দেখার সময়ে কালেক্টিভ ফোর্স ব্যাপারটাই কাজ করে না।
পঞ্চমত, স্টোরিলাইন এবং ক্যারেক্টারের সঙ্গে রেশনালি এবং ইরেশনালি এটাচমেন্ট তৈরি হওয়া। এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য, যা অর্জনে পূর্বোক্ত ৪টি এলিমেন্ট একত্রে কাজ করে। ছোট স্ক্রিনেও এটাচমেন্ট তৈরি হয়, তবে ওই ৪ উপকরণের তীব্রতাগত স্বল্পতায় এটাচমেন্টও প্রগাঢ় হয় না।
চার নম্বর পয়েন্টে কিছু কমতি থাকলেও বাকিগুলোতে দাগির স্কোর উচ্চ, আমার বিবেচনায়, তাই একে কোনোভাবেই ওটিটি ম্যাটেরিয়াল বলা যায় না, বরং ‘দাগি’ এবং ‘বরবাদ’ দুটোই দেখেছি জেনে কেউ যদি অফার করে তার সঙ্গে একটি ফিল্ম পুনরায় দেখতে, আমি নির্দ্বিধায় দাগিকে বেছে নিব।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা থেকে এক রিপোর্টার ফোন করলো, বাংলা সিনেমায় কালচারাল তেলুগুবাদ বিষয়ে আমার ভাবনা জানতে চায়।
দাগির স্টোরিলাইন ক্রিটিকালি ননলিনিয়ার এবং মাল্টিলেয়ারড, তবে শতভাগ স্থানীয় মানুষের গল্প। আমরা গল্পটা কোন ক্যারেক্টারের বয়ানে শুনছি, তার ভিত্তিতে পুরোপুরি কনট্রাস্টিং পারসপেক্টিভ তৈরি হবে, এবং ইন্টারেস্টিংলি প্রতিটি ক্যারেক্টারকেই মনে হবে পলিটিকালি কারেক্ট। বাংলা সিনেমায় স্টোরিটেলিংয়ে প্রায় সকল ক্যারেক্টারের পলিটিকালি কারেক্ট থাকা অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।
গল্পটা যদি মুনিরা মিঠু তথা খুন হওয়া সোহাগের মায়ের লেন্সে দেখি, প্রটাগনিস্ট নিশান তথা আফরান নিশোর প্রতি ঘৃণাকে ভীষণরকম মানবিক হয়। একমাত্র পুত্র বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই খুন হলো নববধূর প্রাক্তন প্রেমিকের হাতে। খুনটা ইচ্ছাকৃত হোক বা দুর্ঘটনাক্রমে তাতে কি শোকের পরিমাণে হেরফের ঘটবে। খুনী যদি ২৫ বছর জেল খেটে তার সামনে আসে, তবু কি ঘৃণা কমে, এবং যদি জানতে চাওয়া হয় আপনি কি ন্যায়বিচার পেয়েছেন, তার ‘হ্যাঁ’ বলার অবকাশ অতি সামান্য। এখানে কোনোপ্রকার যুক্তি কাজ করে না। শুধু খুনীকে নয়, পুত্রবধূকেও স্বাভাবিকভাবে নেয়া তার জন্য অসম্ভবপ্রায়, তাকে দেখলেই মনে হবে এই মেয়েটার সাথে ছেলের বিয়ে দিয়েই এত বড় ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো।
মবশেঠ ওয়ার্ড কমিশনার এবং নিশানের বোনজামাই দুয়ের লেন্সে দেখলে গল্পটা আরো বিস্তৃত হয়। একজন অপরাধী যদি ক্ষমতাবানের আশীর্বাদপুষ্ট না হয় তার সামাজিক পুনর্বাসন অসম্ভব, মব জাস্টিসে সে প্রতিনিয়ত নিহত হবে এবং বাধ্য হবে পুনরায় অপরাধের জীবনচক্রে ফিরতে। ওয়ার্ড কমিশনার নিশানকে এলাকায় থাকতে দিবে না, সে কি নিহত সোহাগের প্রতি সমব্যথী, ১৪ বছর পরেও? নিশানের বাবা যদি নিম্ন আয়ের মানুষ না হয়ে এলাকার প্রভাবশালী কেউ হত, প্রতিবাদের মুখে যদি তার জেলও হত, কমিশনার নিজেই মবকে শান্ত রাখত৷ অথবা নিশান যদি তাকে দিতে পারত টাকা, তাতেও মব উস্কে দিত না। যেহেতু কোনোটাই হলো না, নিশানকে ব্যবহার করে সে খুচরা জনপ্রিয়তা আদায় করে নিয়েছে মাত্র।
নিশানের কনট্রাক্টর বোনজামাই গণ্যমান্য অতিথিদের সামনে যদি তার প্রকৃত পরিচয় দিত, তার ব্যবসা লাটে উঠতো৷ কিন্তু নুশান যদি বাডির সামনে পাজেরো থামাত, অতিথিরা তার ব্যাকগ্রাউন্ডকে বিচার করত গাড়ির মডেল দিয়ে। বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানেই কেউ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা কেন হস্তান্তর করে না– তার প্রকৃত কারণ অনুধাবনযোগ্য হয় এসমস্ত মবশেঠ এবং সামাজিক প্রাণী নামক মেষশাবকদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন পর্যালোচনা করলে।
মন্দ চরিত্র রনজিত সিং তথা শহীদুজ্জামান সেলিম, এবং রবি তথা রাশেদ অপুর চোখে যদি দেখি গোটাটা, সেলিমকে অধিক শিল্প রসিক এবং মানবিক মনে হয়। নিশানকে সর্বসময় সাপোর্ট করে গেছে, শায়েরি শুনিয়েছে, এবং জেলমুক্ত নিশান যখন সাধারণ জীবনে ফিরতে চায় সে সাধুবাদ জানায়৷ এগুলো গ্যাংলিডারের চরিত্রের ব্রাইট লেয়ার হলে,,ক্রুয়েল লেয়ার থেকেও তার একশনকে বুঝতে হবে। গ্যাংলিডারেরা প্রতিপক্ষের চাইতেও ভয় পায় ইন্টারনাল স্পাইদের, প্রায় সকল গ্যাংস্টার কুপোকাত হয় স্পাইদের বেঈমানীর কারণে। তাই গ্যাং চালানোর প্রথম শর্তই ট্রাস্টহীনতাকে ট্রাস্ট করা এবং বেঈমানীর প্রতি সর্বোচ্চ নৃশংসতা। দুজন অস্ত্রবাজ যখন মুখোমুখি হয় ট্রিগারে প্রথম চাপ যে দিতে পারে সে ই বিজয়ী, মোরালিটি সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে অপু আর সেলিমের মধ্যকার অস্ত্রবাজিকে সেই আঙ্গিকে দেখা যায়, দর্শক জানে বেঈমানী করেছে তার গ্যাংয়ের সদস্য তুহিন, সেলিমের কাছে নিশোকে বেঈমান না ভাবার একটিও কারণ ছিল না। তাই ব্যাকলাশ হিসেবে পরবর্তীতে সে যা করেছে, যে কোনো গ্যাংলিডারের টেম্পলেট একই হত।

অপর মন্দ মানুষ রাশেদ অপুর বিত্তর উৎসই বেঈমানী। এরা নিজের বাইরে কাউকে চেনে না, স্বার্থোদ্ধারে চরম নীচতার পরিচয় দিতেও দ্বিধায় ভুগে না। এ ধরনের মানুষ চিরকালই সিস্টেমের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়, নতুন ধান্ধা করে। আমরা অনুমান করতে পারি মাস ছয়েক পরে সে দেশে ফিরবে শিশুপুত্রসহ, পুনরায় তমা মির্জার সাথে সংসার করবে, তমার কিশোরী কন্যাকে সুযোগ পেলে ধর্ষণ করবে, সব আগের মতো।
তমা মির্জার গোলকে যদি তাকাই৷ এক অস্থিতিশীল সম্পর্ককে সে বয়ে বেরিয়েছে দীর্ঘকাল, পরিবারের সাথে যুদ্ধ করেছে, বিয়ে আটকে রেখেছে, প্রেমিকের বাসায় গিয়েছে, প্রেমিক নিখোঁজ, সিরিয়াসনেসের অভাব, খোদ বাবাই বলছে তার ছেলেকে দিয়ে সংসার হবে না। ভার্জিন নয়, পাত্রকে জানিয়েছে, তার সাথে সেটেল হতে চেয়েছে। এরপরে প্রেমিক উদয় হয়ে যদি তাকে চার্জ করে, তাকে দোষ দেয়া যায়? তার সংসারের ব্যাপ্তিকাল বলা হয়নি, তবে তারিখের হিসেব মিলালে ৫-৬ দিন হয়।অতীত আকড়ে না থেকে মুভ অন করতে চাওয়া, মিউচুয়ালি আলাদা হওয়ার নিমিত্তে স্বামী সহ প্রেমিকের সাথে কথা বলতে যাওয়া, প্রেমিকের কাকুতি-মিনতিতে স্বামীকে দূরে দাঁড় করিয়ে একাকী আলাপ করা– এ পর্যন্ত তার আচরণে ফ্ল কোথায়? ক্রেজি প্রেমিক দরজা বন্ধ করে তার সাথে যা করলো সেখানে কনসেন্ট ছিল? ইতোপূর্বে শতবার বন্ধুর বাসায় সংসর্গ করলেও সেটা রোমান্স, কিন্তু ওই মুহূর্তে তা ধর্ষণ, এবং তার প্রেক্ষিতে স্বামীর আসলে করণীয় কী ছিল? প্রেমিককে পেটানো, এবং তমার ধরে নেয়া খুবই স্বাভাবিক নিশোর খুনটা এক্সিডেন্টাল নয়, দুজনের কেউ একজন মরতোই। ফলে নিশোর প্রতি তার অনুভূতিতে ক্রোধ-ঘৃণা-অভিমান সবই থাকার কথা। সে প্রেগন্যান্ট, অথচ নিশ্চিত নয় সন্তানের বাবা কে! মফস্বলের সম্ভ্রান্ত পরিবারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে সেই মেয়ের জীবন নরক হয়ে উঠবে যদি না সে ফাইন্যান্সিয়ালি স্বনির্ভর হয়। হলেও এলাকা ত্যাগ করতে হবে। স্বনির্ভর না হলে যা হয়, বাপের বন্ধু-ছোট ভাই-মামা চাচা গোত্রীয় সকল ধরনের পুরুষের থেকে প্রস্তাব আসতেই থাকে৷ শেষমেষ পয়সাওয়ালা কোনো রুচিহীনের সাথে রুম শেয়ারের লাইসেন্স নেয়।
এমন একটা জীবন কি সে ডিজার্ভ করে?
যদি সবগুলো পারসপেক্টিভকে সমন্বিত করি, মোহনায় পাই প্রটাগনিস্ট নিশোকে৷ তাকে বুঝতে গল্পের টাইমলাইন সিগনিফিক্যান্ট এক উইটনেস। ২০০৮, ইউটিউব শুরু হয়েছে মাত্র, ফেসবুক আসছে, টুইনটাওয়ারে হামলার পরে বিশ্বজুড়ে ওয়্যার এন্ড টেরর চলছে, বাংলাদেশে ২ বছর আর্মি নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলার পরে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামিলীগ। এ সেট আপ এ মফস্বলের এক তরুণ শর্টকাটে বড়লোক হওয়ার জন্য সীমান্তে স্মাগলিং করছে।
মোটিভ কী? সে সহপাঠীর প্রেমে পড়েছে, যে সুশ্রী, বাবা ইঞ্জিনিয়ার এবং উচ্চবিত্ত, সুতরাং এই মেয়েকে বিয়ের একমাত্র উপায় নিজে টাকার মালিক হওয়া, পন্থা যেটাই হোক। সে বুঝে গেছে চাকরির অপেক্ষায় থাকলে সমবয়সী প্রেমিকা হাতছাড়া হয়ে যাবে, আবার বাবারও দৌলত নেই যা তার ব্যাক আপ হতে পারে।
২০০৮ এ ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার শেষ করেছি, তাই নিশো চরিত্রটা আমার সমসাময়িক, ২-৩ বছরের সিনিয়র। আমাদের ওই দিনগুলোতে সমবয়সী প্রেমগুলোতে অধিকাংশ ছেলেদের প্রচন্ড পীড়নের মধ্যে থাকতে হত, কারণ মেয়েটা সেকেন্ড ইয়ারে উঠবার আগে থেকেই নানা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতেই থাকে। আমি একজনকে চিনি, যে ইন্টারে পড়াকালেই কোচিংয়ে ক্লাস নিত, ভার্সিটিতে উঠে ইন্স্যুরেন্স এর চাকরিতে ঢুকে, পত্রিকায় লিখে— এত কিছুর চাপে রেজাল্ট যায় তলানীতে। এখনকার সিনারিও বরং অনেক চার্মিং লাগে, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই সর্বোচ্চ স্ট্রাগল করে।
সীমান্তে গুলি খেয়েও টাকা কামানোর একমাত্র কারণ তমা, সে যদি অন্যত্র বিয়ে করে ফেলে, তাকে গদ্দারই মনে হবে। যদি তার ২৫-২৬ বছরের জীবনকে পাইচার্টে ফেলা হয়, সেখানের ৯০% দখল করে রাখবে তমা। সুতরাং তাকে হারালে ব্রেইন বিকল হওয়ারই কথা।
অন্তিম ক্লাইম্যাক্স। তমার কন্যাকে অপহরণ করা হয়েছে, তাকে ফেরত পেতে হলে নিশোর জীবন দিতে হবে। এতদিন পর্যন্ত নিশোর দৃঢ় বিশ্বাস কন্যার বাবা সে, ডিএনএ রিপোর্ট বলছে সোহাগ। তবু সে মৃত্যুই বেছে নেয়।
এই ডিলেমার প্লাটফরম প্রস্তুত হচ্ছিল সিনেমাজুড়ে। নিশোর বাবা বারবার বলছে জীবনের একটা লক্ষ্য থাকা উচিত, ওদিকে নিশো সবার কাছে শুধু ক্ষমা চায়। নিশান নামের অর্থ চিহ্ন, তমার কন্যা কুশলী যার সম্ভাব্য বাবা সে, তার মধ্য দিয়ে সে চিহ্ন রেখে যেতে চায়৷ যদি কুশলী হয় সোহাগের সন্তান, তাকে বাঁচানোর জন্য আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। দুটো চাওয়াই নিরেট, যেটাই পূরণ হোক প্রতিক্ষেত্রেই তার উদ্দেশ্য পূরণ, কারণ তার আসলে কেউ নেই!
পারসপেক্টিভগুলো একপাশে রেখে উল্লিখিত পাঁচ এলিমেন্টের চতুর্থটাতে দৃষ্টিপাত করি, যেখানে দাগি কিছুটা ম্রিয়মান।
স্টোরিনির্ভর সিনেমার প্রাণ ইমোশনাল এবং আইকনিক সংলাপ। দাগির সংলাপ অতি গড়পড়তা৷ ‘আল্লাহর দুনিয়ায় সব সুন্দর, ফুল সুন্দর, পাখি সুন্দর…… সংলাপটা বারবার ব্যবহৃত হলেও মন স্পর্শ করেনি৷ ক্ষমা না চাওয়ার বহু ক্ষমতাশালী ক্ষমতা হারাইছে— সংলাপটার সাথে অনেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোরিলেট করেছে হয়ত, নইলে হলের দর্শক এটা শুনে রেসপন্স করার যৌক্তিকতা পাই না।
ফরমুলা ফিল্মে আইটেম গান থাকে, স্টোরিভিত্তিক ফিল্মে এসেছে আইটেম ক্যারেক্টার, সুনেরাহ৷ যারা বোবা হয় তারা সাধারণত কানেও শুনতে পায় না। সুনেরাহ শুনে অথবা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে। তার কমিউনিকেশন মাধ্যম মোবাইল স্ক্রিনে লেখা টেক্সট। মুখে অনুচ্চারিত টেক্সটগুলো সংলাপ হিসেবে পাঞ্চিং দারুণ। সমস্ত জগত নিশোর প্রতি জাজমেন্টাল, সুনেরাহ এর চোখে সে ‘কুত্তামারা হ্যান্ডসাম’, এবং সম্ভবত সেকারণেই তার মুখে ভাষা নেই। কেবলমাত্র নৈ:শব্দই নন-জাজমেন্টাল। আইটেম ক্যারেক্টার হিসেবে সুনেরাহ এর সংযুক্তি বেটার হল এক্সপেরিয়েন্স দেয়।
দাগির স্ক্রিপ্টিং আর ক্যারেক্টারগুলো এতটা ওয়েল-ইকুইপড যে কাস্টিং ডিরেক্টরকে খুব বেশি টেনশন নিতে হয়নি। কয়েক বছর প্রফেশনালি অভিনয় করাদের মধ্য থেকে রেন্ডমলি কাস্ট করলেও ডেলিভারেবল হয়তবা একইরকম থাকত, সুনেরাহ এর কেইসটা বাদে।
যেমন আফরান নিশোর ক্যারেক্টারটা যেভাবে ডিজাইন করা তার জায়গায় অপূর্ব-চঞ্চল যাকেই নেয়া হোক, দর্শক তার প্রতি এটাচমেন্ট বোধ করতোই। আর্টিস্টের স্বতন্ত্র কোনো ফ্লেয়ার অনুভব করিনি। নিশোকে যতই হাইলাইট করা হোক, এটা শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টর’স ফিল্মই হয়ে উঠেছে।
তমা মির্জাকে প্রথম দেখেছিলাম শাকিব খানের এক রদ্দি সিনেমায়, সেখানে শাকিবের এক সংলাপ রূপান্তরিত হয়েছে ট্রলিং উপকরণে- ‘এটাই সাইন্স’; সেই তমা মির্জার এমন ট্রান্সফরমেশন অবিশ্বাস্য বটে। তবে সুড়ঙ্গ, দাগি দুই সিনেমাতেই তার যে ক্যারেক্টার, এই ধারা চলমান থাকলে সে টাইপড কাস্টিং হয়ে উঠতে পারে।
ফিল্মের গানগুলো সাদামাটা৷
তাহলে কোন কারণে দাগি দ্বিতীয়বার দেখব, সুযোগ এলে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের সাথে কানেক্টেড বোধ করা, এবং প্রতিটি পৃথক পারসপেক্টিভ থেকেও একই কমফোর্টে গল্পটা ব্যাখ্যাযোগ্য থাকে৷ কালচারাল তেলুগুবাদকে পাশ কাটিয়ে গভীরভাবে স্থানিক এক গল্প বলে, যেখানে সোশিও ইকোনমিকাল এবং কালচারাল কনটেক্সটগুলো নিখুতভাবে তৈরি করে অর্কেস্ট্রা।




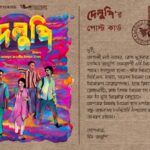

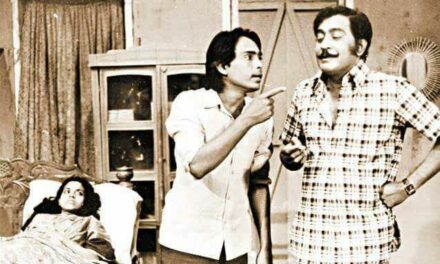












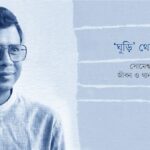
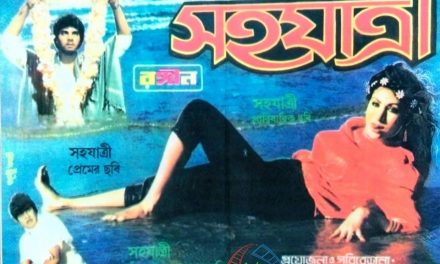

![মাহীকে নায়িকা হিসেবে অপছন্দ ডিপজলের [ভিডিও]](https://bmdb.co/wp-content/uploads/2013/10/Dipjol_1.jpg)