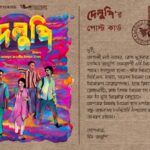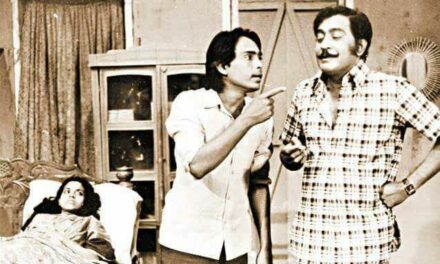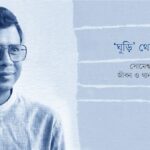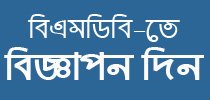ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফি : জ্ঞাননির্মাণের নিরঙ্কুশ আধিপত্য হিসেবে একে থামানো দরকার
পূর্বসূত্রের খোঁজ
১৯৯৭ সাল থেকেই কোনো না কোনোভাবে একটি আলোকচিত্র প্রতিষ্ঠানের১ সঙ্গে গবেষণাধর্মী কাজে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৯৮-৯৯ কালে প্রতিষ্ঠানটি এর শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়, এবং সুবাদে সংবাদ— আলোকচিত্র পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরির কাজগুলো করতে হয়। সম্পর্কিত থাকার কারণে এই পর্বকালটার সংবেদ, সংশ্লেষ ও সংঘাত আমার স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। অনেকগুলো পাঠক্রমই, সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে, আমার অগম্য ছিল— যেগুলো আলোকচিত্রের কারিগরি ও দক্ষতা বিষয়ক। সেই অর্থে আমার সংযোগ সঙ্গতকারণেই ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে এমন বিষয়গুলোর সঙ্গে।
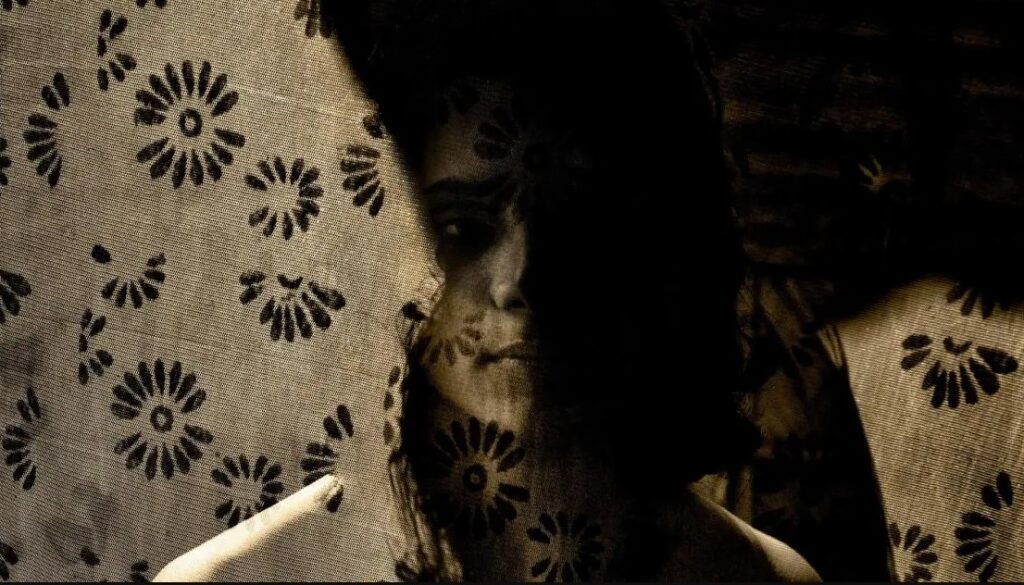
ছবি সূত্র: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
নানান কোর্সের মধ্যে একটার নাম প্রস্তাব হলো ‘ভিস্যুয়াল এ্যানথ্রপলজি’ যেটা পড়াবার দায়িত্ব আমারই ছিল। কোর্সটির নাম এভাবে রাখার ক্ষেত্রে আমার প্রাথমিক কিছু সংশয় ছিল। কিন্তু নানান কারণে শেষে এই নামটা বহাল রাখাই আমার আগ্রহ হয়েছে এবং সেভাবেই পাঠ্যসূচিতে থাকল। এখানে চিত্তাকর্ষক বিষয় হলো, যেসব কারণে আমার সংশয় ছিল ঠিক সেসব কারণেই আমি পরিশেষে এই নামটা রাখতে চাইলাম। কারণটা নিহিত আছে আসলে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট আধিপত্যের মধ্যেই। এই পর্যন্ত এসে আমার পক্ষে জরুরি হয়ে পড়েছে ‘ভিস্যুয়াল এ্যানথ্রপলজি’ এবং ‘ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফি’র মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্ক বা ভিন্নতা নিয়ে সজাগতা ব্যক্ত করা। এথনোগ্রাফি পদটির মধ্যেই রচনাকার সত্তা সন্নিবেশিত আছে। প্রচলিত অর্থে সেটা লিপিগত রচনাকে ইঙ্গিত করে। ‘টেক্সট’ বিষয়ক নয়া ক্রিটিক্যাল ভাবনার মধ্যে চিত্রাবলীকে রচনাকার দায়দায়িত্ব দিয়ে দেখা হয়। সেই অর্থে ছবিমালার মধ্য দিয়ে রচনাকেই ‘ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফি’ পদমালা দিয়ে বোঝানো হয়। আর নৃবিজ্ঞানের যে অংশে এই বিষয়টি সাধিত হয় তাকে ‘ভিসুয়্যাল এ্যানথ্রপলজি’ বলা হয়ে আসছে। মোটামুটি এই পদবিভাজনের মধ্যে যেটা স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে দলিল-দস্তাবেজ উৎপাদন করার ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যেই একটা শাস্ত্রীয় পাটাতন দাঁড়িয়ে আছে। ফলে, বিদ্যাজাগতিক তাগিদেই, সেই দস্তাবেজ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সপ্রশ্ন খতিয়ান আবশ্যক।
আপত্তিটা পদ্ধতিগত
ভিস্যুয়াল এ্যানথ্রপলজি ঐতিহাসিকভাবেই সাক্ষ্যদানকারীর দায়িত্ব পালন করে এসেছে। এই ভূমিকাটা আসলে খোদ আলোকচিত্রের প্রায়োগিক দিকের সঙ্গেই সম্পর্কিত। ঔপনিবেশিক শাসনকালে আলোকচিত্রের প্রাযুক্তিক ও বাণিজ্যিক বিকাশ উপনিবেশের কর্ণধারদের সুযোগ দিয়েছিল উপনিবেশিত প্রজাদের নিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষ উপায় উদ্ভাবনের। সেই হিসেবে রাষ্ট্রীয় নথিপত্রাদিতে প্রজাদিগের ফোটোর সংশ্লেষ গুরুতরভাবে শাসনব্যবস্থার গুণগত অবস্থান্তর ঘটায়। সম্ভাব্য ‘অপরাধীদের’ ক্ষেত্রে যুক্তিটা যত সহজে অনুধাবনযোগ্য, ‘সাধারণ’ জনগণের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কিন্তু শাসনব্যবস্থায় জনগণ কতোটা ‘সাধারণ’ সেটা হালের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বারংবার খতিয়ে দেখা হয়েছে। ফলে আলাপটি একদম নতুন নয়। এখানে উপনিবেশের প্রসঙ্গটাও স্পষ্টতাসাপেক্ষ। কিছু চিন্তক বারবার আনলেও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রসঙ্গটা না-উল্লেখ করবার মতো লঘু করে দেখা যাচ্ছে না। যে প্রশ্নটা এখানে আনা যায়, ফোটোর আগমন কি ইউরোপীয় শাসনব্যবস্থাকে খোদ নিজ প্রজাদিগের নিয়ন্ত্রণে নয়া হাতিয়ার সরবরাহ করেনি? আলবৎ করেছে।
কিন্তু ইউরোপের নিজ প্রজাদিগের শাসনে আলোকচিত্রের এস্তেমাল আর ঔপনিবেশিক প্রজাদিগের শাসনে এর প্রয়োগ গুণগতভাবেই ভিন্ন, এবং পদ্ধতিগতভাবে এ দুইকে আলাদা রাখা জরুরি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শাসকেরা কেবল একটা অজানা এলাকাতেই প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে তা নয়, বরং দস্তাবেজ বানানোর এই কারিগরিটা খোদ শাসিত মানুষজনের কাছেও অজানা একটা বিষয়। শাসনের হাতিয়ার হিসেবে আলোকচিত্রের ব্যবহার তাই সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রান্তে স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। নানাবিধ ‘অপরাধী’ শনাক্ত করা, সম্ভাব্য ‘বিরুদ্ধচারী’দের নথিভুক্তকরণ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ অনুধাবন সহজতর, আগেই যেমনটা বলেছি। কিন্তু আলোকচিত্রের স্বাক্ষ্যদানকারী ভূমিকা এর থেকে আর পরিব্যপ্ত একটা প্রসঙ্গ। জমির হস্তান্তর থেকে শুরু করে বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করতে যাওয়া; বার্থ সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে এমনকি কবরখানার জমি বরাদ্দের জন্যও যে ফোটোর দরকার পড়ে হাল আমলে তার সুনির্দিষ্ট সূচনা ঘটেছে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এবং ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে।
মূল জিজ্ঞাসাটাতে এখানে ফেরা দরকার। স্বাক্ষ্যদানের জন্য ওরফে প্রামাণ্য হিসেবে আলোকচিত্র যেভাবে রাষ্ট্রীক হাতিয়ার হয়ে আসছিল ভিস্যুয়াল এ্যানথ্রপলজি মূলগতভাবে, এবং অন্ততঃ প্রাথমিক কালে, তার থেকে ভিন্ন কিছু করেনি। এর ভূমিকা ছিল পরিপূরকতার— অন্য সংস্কৃতি রচনার টেক্সচুয়াল অনুশীলনের; এর প্রকাশভঙ্গি ছিল সত্যনির্মাণের— র্যাশনাল ইউরোপের দার্শনিক প্রকল্পের; এর পাঠকবর্গ ছিল পয়লায় ইউরোপের কিতাবশিক্ষিত মানুষজন এবং এখন রয়েছে তামাম দুনিয়ার আধুনিক শিক্ষায় উদ্ভাসিত মানুষ তা সে ভৌগোলিকভাবে যে জায়গারই হোক না কেন! ‘অন্য সংস্কৃতি’ রচনায় জ্ঞানগত তাগিদ কী ছিল এবং তা কতটা খাঁটি তা নিয়ে অনায়াসেই বিদ্যায়তনিক লোকজন আলাপে বসে যেতে পারেন। কিন্তু ‘অন্য সংস্কৃতি’ রচনার যে ক্ষমতাগর্বী ভিত্তি সেটা নিয়েই আমাদের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা। এসূত্রে, ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফি মূলতঃ এথনোগ্রাফি বা সংস্কৃতি রচনার একটা সম্পূরক প্রক্রিয়া। আধিপত্যশীল একটা শাস্ত্রের একটা পদ্ধতি, মেথড, কৌশল বা উপায়। সংস্কৃতি রচনার উচ্চম্মন্যতা এবং রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক অন্তর্ঘাত তাই এই মেথডের সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে আছে। এই পদ্ধতির ভূমিকাকে মোকাবিলা করবার জন্য তাই পদবাচ্যগতভাবেই একে অস্বীকার করা ছাড়া পথ নেই।
আবার এর একজন হয়ে ওঠাও একই কারণে
কিন্তু ঠিক যে পরিপ্রেক্ষিতে ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফিকে একটা অনুশীলন হিসেবে মোকাবিলার প্রয়োজন পড়ছে সেই একই পরিপ্রেক্ষিত কারণ তৈরি করেছে এই চর্চারই একজন হয়ে ওঠার। প্রায়শই, আমি সামাজিক নৃবিজ্ঞানের ছাত্র বলে, লোকজন জিজ্ঞেস করেন, এমনকি সাম্প্রতিক কালেও, এমনকি বিদ্যায়তনের মানুষজনও— ‘আচ্ছা! আপনারা তো নৃবিজ্ঞানের লোক; হাড্ডি দেখেই তো বংশ বলে দিতে পারেন।’ উদ্ধৃত বাক্যটি হয়তো পরিস্থিতির সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ একটা চিত্র দেয়। কিন্তু অনুধাবনের গড়পড়তা পরিকাঠামো এর থেকে খুব ভিন্ন না। প্রাথমিক বিবেচনায় মনে হতে পারে যে একটা শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে এরকম প্রশ্নমালা আসে। কিন্তু প্রগাঢ়ভাবে বিষয়টাকে খতিয়ে দেখলে খোদ নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাসের সঙ্গেই একে সম্পর্কিত করে দেখা যায়। যেকোনো শাস্ত্রের পাবলিক আদল তৈরি হবার নানান রকম বিধিব্যবস্থা চতুষ্পার্শ্বে আছে। কিন্তু খোদ শাস্ত্রটির প্রাথমিক দাবিনামাগুলো গুরুতর আছর ফেলতে পারে। একটা দীর্ঘকালীন এবং আন্তর্মহাদেশীয় পথ পাড়ি দেবার পরও সেই দাবিনামাগুলোর বিচারেই পাবলিক একটা অবয়ব তৈরি হয়ে যায়। এ্যাকাডেমি এমনই ভয়ঙ্কর মাল। নৃবিজ্ঞান শাস্ত্র কিংবা এর এথনোগ্রাফি-অনুশীলন এরকম দুর্ঘট পাকানোর ক্ষেত্রে আরও সমর্থ শাস্ত্র— ইউরোপের ‘অন্যে’র প্রতি এর পেশাদার অনুসন্ধানী (নাকগলানো যদি নাও হয়) মনোভাবের কারণে। এটা সাম্প্রতিক কালের শাস্ত্রগুলো দিয়ে আরও সহজে বোঝা সম্ভব— ধরা যাক, দক্ষিণ এশীয় অধ্যয়ন, আফ্রিকীয় অধ্যয়ন কিংবা মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন ধরনের পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা জ্ঞানকাণ্ডগুলো। এখন ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান কিংবা লেবানন নিয়ে, এমনকি বাংলাদেশে বসেও, আর কোনো ফ্রেমওয়ার্ক নয়, শ্রোতা খুঁজে পেতে চাইবে একজন মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ— বলাই বাহুল্য, যে বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করে কোনো একটি মার্কিন বা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। এটা একটা জবরজং হেজেমনিক পরিস্থিতি।
যে উদাহরণটি নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটার ধরে আগানো যাক। ধরা যাক কথিত ওই প্রশ্নের উত্তর দিলাম ‘জ্বি না, আমার নৃবিজ্ঞানী হবার খায়েশ নাই। নেহায়েৎ চাকরি করি।’ ইত্যাদি। এতে প্রশ্নকারীকে থামানো হলো বটে কিন্তু হাড্ডিমূলক বংশবোধ নিয়ে তর্ক করার রাস্তাটাও বন্ধ করা হলো। সেটা যদি আমার আগ্রহ না হয় তাহলে বিকল্প, কিন্তু আরও কার্যকরী-সংমিশ্রণী উত্তরটা আমার আবিষ্কার করতে হয়: ‘হাড্ডি মাপার নৃবিজ্ঞান আমি অনুশীলন করি না।’ এরকম একটা উত্তর সততই ঘাড়ের উপর বোঝা বহন করার একটা বেহুদা সূচনা। কিন্তু শাস্ত্রীয় তর্কটা জারি রাখতে চাইলে, এমনকি প্রায় প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেও, এটা করা ছাড়া উপায় নেই। তখন উদ্যমী প্রশ্নকারী, বিহ্বলতা কাটিয়ে, হয়তো আবার কইবেন: ‘ক্যান ক্যান নৃবিজ্ঞানে এগুলা করে না?’ এই প্রান্তে তখন জাত্যাভিমানী ইউরোপীয় আদিকালের নৃবিজ্ঞান নিয়ে দু’চার কথা বলবার সুযোগ হবে। আলাপ যদি আদৌ কার্যকরী রাস্তা নেয় তখন স্বদেশী সামাজিক বিজ্ঞান চর্চাতেও তাত্ত্বিক পূর্বানুমান, প্রবল জাতির দৃষ্টিভঙ্গি, শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি জটিল জিজ্ঞাসাগুলো খোলতাই করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অনুমান করা যায়, ওই প্রান্তের উৎসাহী প্রশ্নকারী ততক্ষণে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজছেন। কিন্তু এই পরিত্রাণ-আকাঙ্ক্ষাও খোদ জিজ্ঞাসাটির সঙ্গে একটা স্পষ্ট সম্পর্ক। এই স্পষ্ট সম্পর্ক দাঁড় করানোর জন্য আমার পক্ষে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হিসেবে সংমিশ্রিত ভূমিকা নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না, সেটা ক্লান্তিকর হলেও।
ভিস্যুয়াল এ্যানথ্রপলজি বা ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফি শাখার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটাও এরকম। এখানে মুখ্য বিবেচনার বিষয় ছিল পাশ্চাত্যের যেসব পেশাজীবী ঢাকায় কর্মসূত্রে আসেন এবং নিজেদের কোনো না কোনোভাবে ভিস্যুয়াল এথনোগ্রাফির সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার, প্রয়োজনে তর্ক করবার, একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় সমুন্নত রাখা। আধুনিক কালে সবচেয়ে সহজে কোনো আলাপচারীকে খারিজ করে দেয়া যায় তাঁর শাস্ত্রীয় পরিচয় বিবেচনা করে, এবং এভাবেই আধুনিক কালে বিতর্কের নিয়মিত মর্মান্তিক মৃত্যু রচিত হয়ে থাকে।
কিন্তু ভিস্যুয়ালের সাথে তাহলে সম্বন্ধটা কী?
প্রায়শই পেশাজীবীরা দাবি করছেন যে তাঁরা ভিস্যুয়াল প্রামাণ্যকরণ করছেন সামাজিক বিজ্ঞানী হিসেবে কিংবা নৃবিজ্ঞানের চোখে। প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্যীয় পেশাজীবীদের কথা উল্লেখ করলেও এটা পরিকাঠামোগত বা ফ্রেমওয়ার্কের প্রশ্ন। এই পরিকাঠামোটি স্থানীয় পেশাজীবীও গ্রহণ করতে পারেন, বাস্তবে হরহামেশাই তা করেন—তা তাঁরা আলোকচিত্রী হোন, চিত্রকর হোন কিংবা উন্নয়ন গবেষক। সংগৃহীত ভিস্যুয়ালকে তাঁরা সংগ্রশালার কিংবা আর্কাইভ্যাল গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চের খাঁটি স্বাক্ষ্য হিসেবে সেই ভিস্যুয়ালকে বিবেচিত করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রামাণ্যটি ব্যবহৃত হয় আসলে খোদ গবেষকের পূর্বানুমান এবং প্রিজ্যুডিসগুলোকেই প্রতিষ্ঠিত করতে। অন্য ভাষায়, ভিস্যুয়াল নিয়ে আমাদের সতর্কতার জায়গাও খোদ ওখানেই।
ভিস্যুয়াল সত্য ও বাস্তবতার স্বাক্ষী নয়। ভিস্যুয়াল নিজে বাস্তবতার এক একান্ত রূপকার। নিরন্তর বিজ্ঞাপনী ভিস্যুয়ালের দৃষ্টিস্রোতে থাকার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে এটা অনুধাবন অনায়াস। বাস্তবতা নির্মাণ করার এই সামর্থ্যরে কারণে ভিস্যুয়ালকে স্বাক্ষী না মেনে কারক মানতে হবে। সমকালীন ভিস্যুয়াল দুনিয়ার জটিলতার মধ্যে এটাই পয়লা ধাপ।
১. দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার। পরবর্তীকালে পাঠশালা: সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফোটোগ্রাফি নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই সংগঠন গড়ে তোলে। বাংলাদেশের আলোকচিত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে কেবল উত্তুঙ্গ ভূমিকাই নয়, পাশ্চাত্যীয় দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের জন্যও দৃক-পাঠশালা যুগপৎ তাৎপর্যপূর্ণ আত্মপরিচয় গড়ে তোলার বড় একটা দায়িত্ব পালন করেছে।
(ছোট এই রচনাটিও নিমন্ত্রিত ও প্রকাশিত রচনা; কিন্তু কোথায় তা মনে নাই।)
প্রকাশনাসূত্র: বিস্মৃত, তবে ইমেইলে খুঁজে মনে হলো তুষার আবদুল্লাহকে পাঠানো জুন ২০০৯-তে। চিঠি পড়ে মনে হয় তাঁর কোনো একটা খোলা নিমন্ত্রণে, তাহলে তাঁর সম্পাদিত কিছুতে। – ০৩ এপ্রিল ২০২৩)