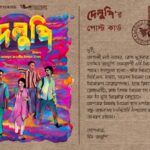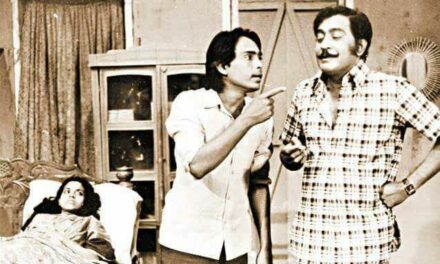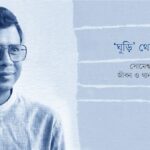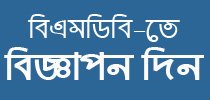ওহে সিনে-পূজারীবৃন্দ!
শাহরুখ ও আমি
জানা মতে তিনি আমার থেকে বছর চারেক আগে জন্মেছেন। কী করা! এতে তো আর আমার হাত নেই। কিন্তু সেটা বড় বিষয় নয়। বিষয় হলো তিনি যখন টিভিতে কাজ পেলেন ও শুরু করলেন তখন আমাদের বেশ এরশাদ-ছুটি হতো; আর মেহেরপুরে বিটিভির থেকে দূরদর্শনের সিগনাল ভাল হতো এবং তাঁর ‘ফৌজ’ সিরিয়াল চলত। আরও দুয়েকটা সিরিয়ালও তিনি করেছেন। তার মধ্যে এমনকি মণি কউলের সিরিজও আছে। ফলে ওঁর অভিনয়-যোগ্যতা নিয়ে যাঁরা নিন্দুক হতে বদ্ধপরিকর তাঁরা মাথায় রাখতে পারেন কউল সাহেব অভিনয়ে খুব ছাড় দেবার লোক নন। আমার প্রায়শই মাথায় ভ্রান্তস্মৃতি হিসাবে থাকে যেন বা শাহরুখকে ‘চুনৌতি’ (প্রথম খসড়ায় ভুলের মধ্যে ভুল হিসাবে আবার ‘ক্যাম্পাস’ লিখেছিলাম; পরে সংশোধন করেছি) সিরিয়ালে দেখেছি। আসলে তা নয়। এরশাদ-ছুটিতে দেখা সিরিয়ালগুলোর মধ্যে ‘চুনৌতি’ই বেশি দাগ কেটেছিল। সম্ভবত অমিত কুমারের গাওয়া শীর্ষসঙ্গীতটার কারণে।

তাফালিংকার শাহরুখ ও প্রযোজক শাহরুখ
মুম্বই কারখানার ছায়াছবিতে পৌরুষের ইতিহাস প্রায় ইন্ডাস্ট্রির সমান বয়সী। মানে পৃথ্বিরাজের আমল থেকেই। এটা পর্দায় কী দেখা যাচ্ছে কেবল তার বিষয় নয়। পর্দার বাইরে সিনেমা কীভাবে সংগঠিত হচ্ছে তার বিষয়। পর্দায় লাল টুকটুকে গালের শাম্মী কাপুর দেখুন, বেচারী ভঙ্গির দুখি রাজ কাপুর দেখুন, গাড়ি সারাইকারী লম্ফরত কিশোর কুমার দেখুন, রাজদুখী ভরত কুমার দেখুন, চিরহাস্যময় শশী কাপুর দেখুন, শিশুদের মতো মাথা ঝাঁকাতে থাকা দেবানন্দ দেখুন, আসে যায় না কিছু, চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া গভীরভাবে পৌরুষ-কিলবিল একটা বিষয়। বড় তারকাদের মজুরি থেকে শুরু করে স্টারডম, কাউকে সাইজ করা থেকে শুরু করে কোলে নিয়ে ৩ দশক কাটানো সবেতেই। এমনকি মুম্বই ইন্ডাস্ট্রির গ্রহণীয় ও অগ্রহণীয় প্রণয়রাজির দিকে নজর দিলেও এই কিলবিলত্ব প্রকাশ পাবে। সে আরেক আলাপ।
এখানে কোনো পুরুষ নির্মাতা/সংগঠক কারও থেকে অধিক নিষ্ঠুর হতে পারেন; কেউ অধিক কোমল গোলাপময় হতে পারেন। যেমন ধরা যায় সেলিম-জাভেদের জাভেদ সাহেবকে “কোমলকবি” ছাড়া আর কোনো ইমেজ দিতে গেলে লোকে মারবে। কিন্তু তাতে করে তাঁদের প্রায় ৬ দশকের দোস্তি আক্রান্ত হয় নাই। শাহরুখ-আমির-সালমান প্রমুখ ময়দানে আসতে আসতে নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এমনকি প্রযোজকদের ‘জব’ও পুনর্নির্মিত হয়েছে। এই নায়কেরা যে ছবি-প্রকল্পের (ফিল্ম-প্রজেক্টের) কী কী নন, তার হিসাব করাই বরং কঠিন। ফলে কে কার উপর গাড়ি তুলে দিলেন, হরিণ বা বিবেক উবেরয়কে মৃত্যু বা ধামকি দিলেন, কে দুবাইয়ে প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা শুরু করলেন এগুলো আসলে ওই চলচ্চিত্র কারখানার “বাইরের” প্রসঙ্গ নয়। এই তিন খানেরই যে বৈশিষ্ট্যটা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ (হতে পারে) তা হলো চলচ্চিত্রের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে পাশ কাটিয়ে “মাসিভ” দৃশ্য বানানোর ক্ষেত্রে এঁরা নিজ-নিজ স্টারডমের প্রয়োগ করেছেন। আগের প্রজন্মের হিসাবে তা “বদকাজ” হিসাবেই দেখা লাগবে।
এতদসত্ত্বেও, প্রযোজক এবং নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গৌরী-শাহরুখ এবং রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট স্বাক্ষর রাখার মতো প্রতিষ্ঠান। একাধিক নজির আপনারা পাবেন। ‘বিল্লু’ ছবি বানাতে গিয়ে যখন মুম্বাইয়ের অভিজাত কেশবিন্যাসকদের তোপের মুখে “বিল্লু বার্বার” নামটা বদলাতে হয়েছিল শাহরুখের, আমার বেশ মনভারই হয়েছিল। চিত্তাকর্ষক ছবি বটে।
জোয়ান/জওয়ান শাহরুখ
তা এঁরা সকলেই জোয়ানই আছেন। এতে আমাদের হিংসা হওয়া সম্ভব। কিন্তু রাগ করা চলে না; আপত্তি তো কোনোভাবেই নয়। ফলে শাহরুখের এই ছবির নাম ‘জোয়ান’ হতেই পারত। তবে হিন্দিতে বোধহয় ‘যুবা’ না বললে প্যাঁচ লেগে যেত। তার মধ্যে এই ছবির কাহিনি বা নির্মাণে আসলে শাহরুখের হাত ছিল না বলে ধরে নিতে হবে। কেবল গৌরী একজন প্রযোজক। এটা আসলে ‘জওয়ান’ই, বাংলায় সৈনিক। গত ২০ বছর ধরে ভারতের ছবিতে সৈনিক এতবার এসেছেন যে পরের জন্মে গান্ধী ব্যারিস্টার না হয়ে মিলিটারি হতে চাইতে পারেন। আমি তার জন্য তাঁকে নিন্দা করব না।
এখন ভারতীয় মিলিটারি অফিসাররা স্পোর্টসের আগে বাণী দিতে টিভিতে আসেন। আরও কী কী সব কাজে আসেন। সম্ভবত কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলতেও আসেন। সেই তুলনায় আমরা বাংলাদেশে অত দুর্যোগের মধ্যে থাকি না। এখানে একবার এক উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ পুলিশ কেবল নাকে মাস্ক পরতে বলেছিলেন। এটা মহৎ আহ্বান ছিল। নাকে মাস্কের বদলে অন্য কিছু পরতে বললে বরং নিন্দা করতাম। যাহোক ‘জওয়ান’ আমার দেখা হয়নি। আকর্ষণীয় এবং/বা উস্কানিমূলক প্রস্তাব পেলে ভেবে দেখতে পারি।
ভারতীয় সিনেমা
সিনেমা আমদানি নিয়ে এবং বিশেষত ভারতীয় সিনেমা আমদানি নিয়ে যত আর্তনাদ বাংলাদেশে আছে আমি তার অত্যন্ত অসংবেদনশীল গ্রহীতা। নিষ্ঠুর বলতে পারেন, হৃদয়হীনা বলতে পারেন, ‘বাজারের দালাল’ বললেও আমি দুঃখ পাব না কথা দিচ্ছি। দেখেন, যদি সাবান-শ্যাম্পুর কাতারে সিনেমাকে আমি দেখি বলে আপনারা দুঃখ পান; তাহলেও তো অন্তত বইপুস্তক বা সাহিত্য-চিত্রকলার কাতারে রাখবেন? নাকি? বইপুস্তকের বাজারে সিস্টেম্যাটিক কালচারাল “বৈচিত্র্য” বলে কিছু আছে? নাকি ভাষার বেলায় তা সম্ভব? বাংলায় যে গুটিকতক লোক কোনো হীনম্মন্যতা ছাড়াই লিখে বুড়া হয়েছেন, তাঁদের পরের প্রজন্মকে অভিশংসন করতে করতে এবং রিভাইস করাতে করাতে ইংরাজিপুষ্ট/ইংরাজিক্লিষ্ট বানিয়ে ছাড়ছেন আপনারা। আর চিত্রকলার দুনিয়াটা যে সঠিক কই কই থাকে, অধিকাংশ লোকে তো টেরই পাই না। তাহলে রইল এক সিনেমার জগত যেখানে দুচারটা জানালাতে দুচারটা ভাষার ছবি দেখার পরিবেশ রাখা সম্ভব।

আমাদানিকৃত ছবির সারবত্তা, বিষয়বস্তু নিয়ে আপনাদের মতামত থাকতে পারে। বিশ্বাস করুন, যদি তা থাকে, আমি সেই আলাপে যোগও দেব। যত অলসই হই, সরকারের ছবি নির্ধারণ কৌশলে সক্রিয়, মেধাবী (ও অবেতন) পরামর্শক থাকতেও রাজি আছি। কিন্তু সেসব হবার নয়। তাই বলে “অমুক দেশের ছবি আমাদের ছবি খায়া ফেলবে” এই আর্তনাদ ঠিক এই সময়কালের ব্যাকরণের সাথে মানানসই নয়। উপরন্তু, বাংলাদেশে “সিনেমা খায়া” ফেলার জন্য যেসব রাক্ষসকে আপনারা গত ২০ বছর ধরে দায়ী করে আসছেন তা আমার কৌতুকের সীমানা ডিঙিয়ে এখন বিরক্তির সীমানায় এসেছে। স্মৃতি থেকে আপনাদের রাক্ষসগুলো মনে পড়ছে: অশ্লীলতা, কাটপিস, সিনেপ্লেক্স, “গল্পের অভাব”, “রুচির অভাব”. এবং অবশ্যই গত কয়েক বছর ধরে “ভারতীয় ছবি”। ওরে গবা!! গিটারের কাজ যে লাউয়ের খোসা দিয়ে হবে না, এমনকি জিনিয়াসের পাল্লাতেও হবে না, এটা বুঝতে কি প্রাগ বা নিউ ইয়র্কে ফিল্ম ডিগ্রি করা লাগে? বাংলাদেশের সমস্যা সিনেমা হল ও কারখানা বাঁচাতে “রাষ্ট্রীয় অনীহা”; বাণিজ্য-উদ্যোক্তাদের এটার তুলনায় অন্যান্য লাভজনক খাতকে দেখতে শুরু করা, এবং অতি অবশ্যই একটা “ভর্তুকিমূলক জনখাত” হিসাবে একে আবিষ্কারের/নির্ধারণের জন্য সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ না-থাকা। ইত্যাদি।
কেন?! উত্তম-সুচিত্রা হলে দেখার কালেই বাংলাদেশে “জাগো হুয়া সাবেরা” বানানো হয়নি?
নাকি সিনেমা-বন্দনাই আপনাদের জীবনব্রত?
তাইলে আর আমার কিছু বলার নাই। আমাদের যৌবনে কোন কলার থেকে কোনটা শ্রেয়তর এ নিয়ে যুবকেরা কহিয়া গিয়াছেন বহু বহু কথা (বাস্তবেই এসব তর্কে নারী যুবকদের কম আগ্রহ ছিল)। তখন অবশ্য গাছের কলারও ১০ রকমের পদ সুলভ ছিল। তবে কথা হতো পরিসম্পাদনা/পার্ফর্মেটিভ/”ক্রিয়েটিভ” বিষয় নিয়ে। গদ্যের তুলনায় পদ্য যে কত মহান, তা পদ্যকাররা গদ্যকারদের না-শুনিয়ে ছাড়তেন না। থিয়েটারই যে মুখ্য শিল্প সেটা অথিয়েটারকারীদের জানতেই হতো। সকল কলার সেরা কলা যে চলচ্চিত্র তা রাশান বা ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারগামীরা বলতে কখনোই ভুলতেন না। কখনো কখনো সকাল-বিকাল মন্ত্রের মতো করে বলতেন।
কিছু ভাষাও প্রণিধানযোগ্য: “আসল সিনেমা হলো গিয়ে …”, “সিনেমা হয়ে উঠতে গেলে…”, “আমরা যদি ফিল্মের বিচারে ভাবি…”, “সিনেমার যে এইসথেটিক্স তা ধরে বললে…”, “সিনেমাটিক ডেপ্থের আসলে কোনো ছাপ…” মেলা মেলা জোগাড় করতে পারা যাবে। ‘হাই আর্ট’ আর ‘লো আর্ট’ এর এই ভ্যাজর ভ্যাজর মেলা হয়েছে। সঙ্গীতের দুনিয়ায় হয়েছে, সাহিত্যের দুনিয়ায় হয়েছে, চিত্রকলার দুনিয়াতে তো আকছার হয়ে চলেছে এখনও। পরিস্থিতি এত খারাপ যে আজ আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বেঁচে থাকলে তাঁর তীব্র-তীক্ষ্ণ “রঙ্গরস” করার অভ্যাসের কারণে অভিশংসিত হতে হতো (অবমাননা মামলা বাদ দিলেও)। ওরে! (শিল্প/সাহিত্য/সংস্কৃতি) কারখানায় উৎপাদন শুরু হবার পর কারখানার চরিত্রটা তো অন্তত দেখবেন, নাকি?! লক্ষ্য করবেন, “আমার পছন্দ হয়নি” “আমার পছন্দ নয়” বলা আর “আসলের” জয়গান করা আকাশ-পাতাল ভিন্ন।
যদি সিনে-পূজারীই থাকতে চান আপনি/আপনারা, যদি “আসল সিনেমার” বা “প্রকৃত ফিল্মের” একটা বিগ্রহ স্থাপন করে তার সামনে বসে নৈবেদ্য দেবারই নিয়ত থাকে আপনার, তাহলে আসলে আমি দূরেই থাকি বরং। পূজারীদের প্রতি আমার ব্যাপক সম্মান; এতটাই যে আমি সম্ভ্রমভরে দূরে (ও আরও দূরে) থাকব আপনার।
শাহরুখ জোয়ান থেকে কোনো একদিন বৃদ্ধ হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রডাক্টকে ডেইটি বানানোর বদভ্যাস আপনার যাবে না।
(ফ্লুকালে ক্রিয়েটিভিটি। জাবি অফিসঘর। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩। দুপুর ১১.৫৫)