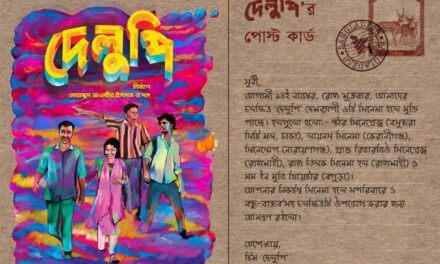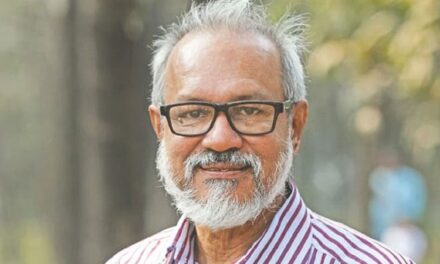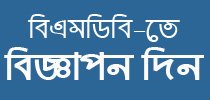বক্স অফিস ও মাল্টিপ্লেক্স কালচার নিয়ে বিএমআরের ফাহিম মুন্তাছিরের সঙ্গে আড্ডা
[বাংলা মুভি রিভিউ বা বিএমআর। ফেসবুক পেজ ভিত্তিক এই কার্যক্রম নিয়ে বলার আগে সিনেমার জগৎ নিয়ে তো বলতে হয়। এখানে খুব ট্রেন্ডি বিষয় হলো বক্স অফিস রিপোর্ট। বাংলাদেশে অফিসিয়াল এ ধরনের কার্যক্রম নেই; তাই বলে চাহিদা নেই এমন নয়। বিএমআরের বক্স অফিস রিপোর্টগুলোয় রিয়্যাক্ট ও মন্তব্যের ঘর দেখলে তা বোঝা যায়। স্বেচ্ছাশ্রমে প্রায় দুই বছর ধরে এ কাজ করে যাচ্ছে বিএমআর। তাদের রিপোর্টের প্রক্রিয়াটিও স্বচ্ছ; কোনো লুকোচুরি নেই। যা এখন মূলধারার সংবাদমাধ্যমের জন্যও তথ্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। এমনকি এরই ধারাবাহিকতায় আজকাল নির্মাতারা বক্স অফিস আয় প্রকাশ করছেন বলেই অনেকের ধারণা। বিএমআরের মূল ব্যক্তি ফাহিম মুন্তাছির। সদ্য স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করেছেন। তার সঙ্গে বক্স অফিস নিয়ে আড্ডায় ছিল বাংলা মুভি ডেটাবেজের কো-অর্ডিনেটর ওয়াহিদ সুজন। সেই আলাপে বর্তমান বাংলা সিনেমার বিভিন্ন দিক ও মাল্টিপ্লেক্স কালচারের কিছু বিষয়াদি উঠে এসেছে। আগ্রহী পাঠকরা সেই দীর্ঘ আলাপে যোগ দিতে পারেন। জানাতে পারেন আপনাদের মন্তব্যও।]

ওয়াহিদ সুজন: সিনেমার বক্স অফিস নিয়ে আমাদের সবারই আগ্রহ আছে। কিন্তু বাংলাদেশে অফিশিয়াল হিসাব পাওয়া মুশকিল। মাল্টিপ্লেক্স থেকে এখন এক ধরনের অনুমিত হিসাব যাচ্ছে, যা আমরা বাংলা মুভি রিভিউর মাধ্যমে পাচ্ছি। তো, আইডিয়াটা মাথায় কীভাবে এলো?
ফাহিম মুন্তাছির: বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলোর বক্স অফিস ডেটা ছিল এই ইন্ডাস্ট্রির শুরু থেকেই একটি বড় ধাঁধা। দর্শক, প্রযোজক, এমনকি ইন্ডাস্ট্রির স্টেকহোল্ডাররাও দেখা যায় তাদের চলচ্চিত্রগুলোর ইনকাম কেমন হচ্ছে এটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না, বা রাখলেও সেটি কিছুটা এড়িয়ে যেতে চান।
গত দশকের বেশকিছু চলচ্চিত্র শুধুমাত্র মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে ভালো সাড়া পেয়ে ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসেবে জয়া আহসান অভিনীত ‘দেবী’র কথা বলা যায়। কিন্তু ‘দেবী’র মতো এরকম আরো কিছু চলচ্চিত্রের সেই সাফল্য সম্পর্কে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট তথ্য না থাকায় অনেকেই এটি মানতে চান না যে, শুধুমাত্র ১০টি মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা চালিয়ে কোটি টাকা ফেরত আনা সম্ভব। ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দীর্ঘদিন আমরা এই তথ্যশূন্যতার অভাবে ছিলাম।
এই শূন্যতা পূরণের জন্য বিএমআর প্লাটফর্মটি ২০২৩ সালের ২৩ জুলাই থেকে ম্যানুয়ালি মাল্টিপ্লেক্সগুলোর ডেটা ট্র্যাক করা শুরু করে। এটি ছিল আমাদের পক্ষ থেকে একটি বড় পদক্ষেপের ছোট্ট শুরু, যা বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াতে ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।
ওয়াহিদ সুজন: এ ধরনের কাজে বিপুল সময় ও মনোযোগ লাগে। নিয়মিত বা দিনের পর দিন যা-ই বলি স্বেচ্ছাশ্রম হিসেবে কঠিনই হওয়ার কথা।
ফাহিম মুন্তাছির: জ্বী। তার সাথে একাগ্রতা ও সততাও প্রয়োজন। সব মিলিয়ে কাজটি খুব কঠিন। তবে যখন আমি দেখছি, আমাদের এই কাজ ইন্ডাস্ট্রির কোনো অংশকে ‘স্বচ্ছতা’ প্রদান করছে। প্রযোজক থেকে দর্শক পর্যন্ত… এমনকি যেসব নতুন ইনভেস্টর এখানে আসার চিন্তা করছেন, সবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করছে, তখন এই কঠিন কাজ করার ক্লান্তিটা পেছনে চলে যায়।
ওয়াহিদ সুজন: যতটুকু দেখেছি শুরুতে ঢাকার নির্মাতাদের কেউ কেউ বিএমআরের বক্স অফিসকে ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যে, এখন বিএমআর নিয়ে অভিযোগ নেই। আবার অনেক সংবাদমাধ্যম নামে-বেনামে আপনাদের দেয়া তথ্য থেকে সংবাদ পরিবেশন করছে। অবশ্য মাল্টিপ্লেক্সগুলোর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। পুরো বিষয়টা কীভাবে দেখেন?
ফাহিম মুন্তাছির: শুরুর দিকে কিছু নির্মাতার সংশয় থাকাটা হয়তো স্বাভাবিক ছিল, কারণ বাংলাদেশে বক্স অফিস ডেটার কোনো স্বীকৃত মডেল পূর্বে ছিল না। আর আমাদের স্বভাবতই নতুন কিছু গ্রহণ করে নিতে একটু সময় লাগে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিএমআরের ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি, বিশ্লেষণের স্বচ্ছতা এবং চলচ্চিত্র পরিবেশকদের সাহায্যে ক্রস-ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা ইন্ডাস্ট্রির আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। এখন মিডিয়া বা স্টেকহোল্ডাররা আমাদের ডেটা রেফার করছে— এটাই প্রমাণ করে যে আমাদের মডেলটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।
মাল্টিপ্লেক্সগুলোর প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া না থাকার কারণ হতে পারে তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি। তবে তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে, যা পরোক্ষভাবে তাদের স্বীকৃতিরই ইঙ্গিত দেয়। আসলে, বক্স অফিস ডেটা নিয়ে কোনো পক্ষেরই ‘এজেন্ডা’ থাকা উচিত নয়— লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি ট্রান্সপারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা, যেখানে ডেটা সবার জন্য সহজলভ্য।
ওয়াহিদ সুজন: হ্যাঁ। আমার মনে হয়, দেশি নির্মাতাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বের দিক হলো সিনেমার বাজেট, দর্শক রুচি সম্পর্কিত তারা সরাসরি এটা ধারণা করতে পারেন। অর্থাৎ লগ্নির ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য জানা যায়। আমরা মূলত বাংলা সিনেমা নিয়েই কথা বলছি। তো, বক্স অফিস ডেটা সংগ্রহের উদ্যোগ বাংলা ইন্ডাস্ট্রির জন্য কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন আপনি?
ফাহিম মুন্তাছির: আমি মনে করি বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে বক্স অফিস ডেটা সংগ্রহের উদ্যোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আমাদের মতো বাজারে যেখানে প্রযোজক থেকে দর্শক সবাই মূলত অভিজ্ঞতা ও অনুমানের ওপর নির্ভর করেন। এখানে তিনটি মূল পরিবর্তন আসতে পারে—
প্রথমত, নতুন প্রযোজক তার বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সহায়তা পাবেন। যদি তিনি কোনো ভিন্ন ঘরানার কাজে লগ্নি করতে চান, তিনি আমাদের ডেটা চেক করে দেখতে পারেন। যেমন মাল্টিপ্লেক্সে ভৌতিক ঘরানার সিনেমা বেশ ভালো ব্যবসা করে, সিনেমার মান যতই জঘন্য হোক। ‘জ্বীন-২’ এর মতো মানে ঘাটতি থাকা ভৌতিক ঘরানার সিনেমা ২০২৪ সালের ঈদুল ফিতরে মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কালেকশন করেছিল। তো ভালোমানের হরর কনটেন্ট নিয়ে আসলে সেটি আরো দর্শক টানবে।
দ্বিতীয়ত, দর্শকদের কাছে তথ্যের স্বচ্ছতা থাকবে। দর্শকরা জানতে পারবেন কোনো সিনেমা আসলেই ‘হিট’ নাকি শুধু মার্কেটিং হাইপ। এতে প্রকৃত দর্শক টানা কনটেন্টকে পুরস্কৃত করা সহজ হবে।
তৃতীয়ত, ইন্ডাস্ট্রির সার্বিক গ্রোথ হবে। ডেটা শেয়ার করলে বড় ইনভেস্টর বা ওটিটি প্লাটফর্মগুলোর আস্থা বাড়বে। তারা দেখতে পাবেন বাংলাদেশি সিনেমার অডিয়েন্স ও রিটার্ন পটেনশিয়াল।
ওয়াহিদ সুজন: বিএমআর যদিও লায়ন বা সিলভার স্ক্রিনের মতো মাল্টিপ্লেক্সের আয় প্রকাশ করে। কিন্তু আইডিয়াল অর্থে একাধিক আউটলেট নিয়ে তৈরি মাল্টিপ্লেক্স এখানে একটাই। স্টার সিনেপ্লেক্স। এখান থেকে আয়ের বেশির ভাগ অংশ আসে। এ বিষয়ে পরে আবার ফিরব। এখন একটু সোসাইটির দিকে ফিরি। অর্থবিত্ত ও রুচির হিসেবে মাল্টিপ্লেক্স মূলত আপার মিডলক্লাস ও আপার ক্লাস কালচার প্রমোট করে। সারা দুনিয়ার মতো সুপারহিরো সিনেমাগুলো এখানেও হিট। যেমন স্টার সিনেপ্লেক্সের ইতিহাসে আমার তুমুল বাণিজ্য করা সিনেমা হিসেবে দেখে গেছে হলিউডের নির্মাণ। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেটা বাংলা সিনেমার দিকে ফিরছে। সেটা নিশ্চয়ই গড়পতার বাংলা সিনেমার বিষয় নয়। এ পরিবর্তনে কী কী বিষয় আছে? যেহেতু আপনারা ট্রেন্ড ও ট্রেড এনলাইসিস করেন, সে দিক থেকে জানতে চাই।
ফাহিম মুন্তাছির: প্রথম যে বিষয়টি, সেটি হলো গল্প বলার ঢঙ্গে পরিবর্তন এসেছে। আমরা একটি লম্বা সময় ধরে দেখেছি যে, একটি বাংলা চলচ্চিত্র সাজানো হতো সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণি কী চায়, তারা কী ধরনের বিনোদন গ্রহণ করে, সেই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে। তখন আমাদের দেশে সিঙ্গল স্ক্রিন বেশি থাকাতে, এই ধরনের চলচ্চিত্র বেশি নির্মিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সেই গল্প বলার ঢঙ্গে পরিবর্তন এসেছে। এখন নিম্নবিত্তের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের চিন্তাভাবনাকে মাথায় রেখেও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ শাকিব খানের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা বলা যায়। এই ঈদে তার দুটি চলচ্চিত্র রিলিজ পেলো। ‘বরবাদ’, যা মাল্টিপ্লেক্সে খুব অসাধারণ রেসপন্স পাচ্ছে, রিপিট দর্শক পাচ্ছে। অন্যদিকে ‘অন্তরাত্মা’, মাত্র দেড়দিন চালানো সম্ভব হলো। দর্শকের অভাবে সবগুলো মাল্টিপ্লেক্স থেকে নামিয়ে দেয়া হলো। সিনেমাদ্বয় দুটি ভিন্ন ধরনের দর্শকশ্রেণিকে মাথায় রেখে নির্মাণ করা হয়েছিল। যদি একটু অতীতে ফিরে যাই, শাকিব খানের একাধিক সিনেমা একসাথে মুক্তি পেলে, নির্মাণগত দিক থেকে যে সিনেমা নিম্নবিত্তকে টার্গেট করতো সেই সিনেমা বেশি ব্যবসা করতো। ২০১৬ সালের কোরবানির ঈদে ‘বসগিরি’ থেকে ‘শ্যুটার’ বেশি ব্যবসা করেছে, ২০১৭ কোরবানির ঈদে ‘রংবাজ’ থেকে ‘অহংকার’ বেশি ব্যবসা করেছে। এরকম আরো উদাহরণ দেয়া যাবে। এর কারণ তখন সিঙ্গল স্ক্রিন বেশি ছিল। কিন্তু এবার সেটির পুনরাবৃত্তি হলো না।
দ্বিতীয়ত, বাংলা চলচ্চিত্রের অনলাইন প্রমোশন আগের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএমডিবি নিজেও এই সাফল্যের অন্যতম অংশীদার, আপনারা ডিজিটাল চলচ্চিত্রের শুরু থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাংলা চলচ্চিত্রের একটি বিপ্লব আনার। আগে একজন সাধারণ দর্শক সিনেমাহলের সামনে না গেলে বাংলা চলচ্চিত্রের নামগন্ধ খুব একটা খুঁজে পেতো না, সেই দর্শক আমি মনে করি এখন বছর শেষে অন্তত পাঁচটি বাংলা চলচ্চিত্রের নাম বলতে পারবে যা সাম্প্রতিক সময়ে রিলিজ পেয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে।
তৃতীয়ত, দেশে বা রাজধানী ঢাকায় মানসম্পন্ন সিঙ্গল স্ক্রিন কমে গিয়েছে। বলাকা, অভিসার, রাজমনি, জোনাকি, চিত্রামহল… প্রায় ৮০০-১১০০ আসনক্ষমতা সম্পন্ন পাঁচটি সিনেমাহল, গত পাঁচ বছরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই সবগুলো সিনেমাহল ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, এদের একটা বড় দর্শক শ্রেণি ছিল তরুণ ভার্সিটিপড়ুয়া শিক্ষার্থী এবং পারিবারিক দর্শকশ্রেণি। এই পাঁচটি সিনেমা হলের দর্শক এখন মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখছে। টিকেটমূল্য বেশি হওয়া সত্ত্বেও অন্তত উৎসবের সময়গুলোতে তাদের ব্ল্যাকে টিকেট কেনার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না, অনলাইনে নিজের পছন্দের সিট দেখে অগ্রিম বুক করে রাখতে পারছে, অনেক ভালো পরিবেশ পাচ্ছে, সাথে টপ লেভেলের সাউন্ড ও পিকচার, সবমিলিয়ে তারা এসময় মাল্টিপ্লেক্সে এসে ভালো বাংলা চলচ্চিত্রগুলো দেখছে।
ওয়াহিদ সুজন: বিএমডিবিতে আমরা সিনেমার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জায়গা থেকে দেখি। এমনিতে জনপ্রিয় গানের হিসাব করলে বাংলা সিনেমার একটা কমন হেরিটেজ কিন্তু টের পাওয়া যায়। যাই হোক, এখানে দুটো বিষয় পাচ্ছি মনে হয়। প্রথমত মানুষ হলে গিয়ে নিজ ভাষায় সিনেমা দেখতে আগ্রহী। কিন্তু সেটার সঙ্গে টেকনোলজির একটা সম্পর্ক আছে, এটা দ্বিতীয় ব্যাপার। দুটো সম্মিলন যখন ঘটছে তখন আগ্রহী হচ্ছে। অবশ্য কী নির্মাণ হচ্ছে সেটা একটা বিষয়। আচ্ছা, বক্স অফিসের আলাপেই ফিরি। আমরা এ আলাপে যেতে যেতে আজ ‘দাগি’র অফিসিয়াল আয় প্রকাশ হলো। এ নিয়ে ঈদের তিনটা সিনেমা (বরবাদ, জংলি ও দাগি) বিভিন্ন সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রস আয়ের তথ্য প্রকাশ করল। আমার অনুমান এখানে বিএমআরের একটা ভূমিকা আছে। আপনারা এ ধরনের তথ্য প্রকাশের পর নির্মাতাদের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হয়েছে। এটা কিন্তু এক ধরনের স্বীকৃতি। যেহেতু সিঙ্গেল স্ক্রিনে বরবাদের রিলিজ বড় পরিসরের। সেটা অনেকটা পরিষ্কার চিত্র দেয় না। কিন্তু মোটের ওপর মাল্টিপ্লেক্সকেন্দ্রিক আয় দেখলে এসব আনুষ্ঠানিক আয় প্রকাশের একটা সত্যতা মেলে।

ফাহিম মুন্তাছির: আমি হয়তো এখন বলতে পারি, বিএমআরের ডেটা স্বচ্ছতার চর্চাকে ইন্ডাস্ট্রিতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। দাগি, বরবাদ ও জংলির মতো সিনেমাগুলো যখন তাদের অফিসিয়াল গ্রোস আয় প্রকাশ করে, তা শুধু সংখ্যার গল্প নয়— এটি দর্শক ও নির্মাতাদের মধ্যে আস্থার সেতুবন্ধন তৈরি করে।
মাল্টিপ্লেক্স-কেন্দ্রিক ডেটার সামান্য কিছু সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই বলছি, এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ট্র্যাকেবল মডেল। সিঙ্গেল স্ক্রিনের ডেটা অসংগঠিত হলেও মাল্টিপ্লেক্সের রিয়েল-টাইম আয় প্রতিবেদন আমি মনে করি একটি বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছে।
আমাদের লক্ষ্য হলো এই ডেটা কালচারকে সম্প্রসারিত করা, যাতে একদিন সিঙ্গেল স্ক্রিনও এই স্বচ্ছতার অংশ হয়। আমরা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ব্লকবাস্টার সিনেমাসসহ ঢাকার সবগুলো সিঙ্গেল স্ক্রিন সারাবছর কভার করা শুরু করবো। এরপর ধীরে ধীরে ঢাকার বাইরে ছড়াবো। আমাদের ইচ্ছা আছে এমন করার। আমি মনে করি এটাই হবে বাংলা চলচ্চিত্রের টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি।
ওয়াহিদ সুজন: আচ্ছা। দাগির ৭ কোটি গ্রসের অফিশিয়াল ঘোষণা প্রকাশের পর একটা পোস্ট দেখলাম ফেসবুকে। সেখঅনে বলা হচ্ছে— বিএমআর কালেকশনের যে তথ্য দেয়, সেটা অনলাইনে টিকিট বিক্রির হিসাব। কিন্তু সিনেপ্লেক্সের কোনো একটি শো শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই সেই অনলাইন বুকিং সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন সিনেমা হলে গিয়ে টিকিট কাটতে হয়। এই এক ঘণ্টার কালেকশন দেয়ার ক্ষমতা বিএমআরের নেই। কমপক্ষে ২৫–৩০ শতাংশ ইনকাম হয় শেষ ঘণ্টায়। মন্তব্যে উঠে আসা বিষয়টা কি বিএমআরের একটা সীমাবদ্ধতা?
ফাহিম মুন্তাছির: যদি সরলভাবে চিন্তা করেন, তবে বলতে পারেন এটি আমাদের একটি সীমাবদ্ধতা। আমরা যখন প্রথমে কোনো নতুন চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন দর্শক সংখ্যা ও শো টাইম বিচার করে আমাদের নিজস্ব সফটওয়্যারের সাহায্য নিয়ে সামান্য কিছু বাড়িয়ে ধরি, সেটি ৫-১৯ জন। তবে সেই চলচ্চিত্রের সিনেমাহল রানিং শেষ হলে, পরবর্তীতে যখন আমরা বিভিন্ন পরিবেশক অফিসে আমাদের রিপোর্টটি ক্রসচেক দিতে যাই, তখন কিন্তু আমরা আবার আমাদের কাছাকাছি একটি রিপোর্ট তাদের কাছেও পাই। আর প্রায় সময় তাদের রিপোর্টে আমাদের থেকেও কম অ্যামাউন্ট লেখা থাকে। তো এই এক ঘণ্টার হিসাবটি কে পায়, আদৌ কোনো প্রযোজক-পরিবেশক পায় কিনা, আমি প্রশ্ন রেখে গেলাম।
তবে আমি আসলে কোনো একক পক্ষকে দোষ দিতে রাজি নই, বরং এটি পুরো সিস্টেমের একটি সমন্বয়হীনতার ফল। মাল্টিপ্লেক্সগুলোর বর্তমান টিকিটিং সিস্টেম শেষ মুহূর্তের ওয়াক-ইন বিক্রি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করতে পারে না। আবার ইন্ডাস্ট্রিতেও ডেটা শেয়ারিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রীতি এখনো গড়ে ওঠেনি। বিশ্বের অনেক বড় মার্কেটেও এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে— ভারতের কিছু মাল্টিপ্লেক্স বা হলিউডের কিছু থিয়েটার চেইন ২০২৫-এ এসে ওয়াক-ইন ডেটা ট্র্যাকিংয়ে অনিয়মিত। সব সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য হলো একটি স্বচ্ছ সিস্টেম তৈরি করা যেখানে প্রযোজক, থিয়েটার এবং দর্শক— সবাই নির্ভরযোগ্য ডেটা পাবে। এজন্য সবার সহযোগিতা জরুরি, কারণ এটি শুধু বিএমআরের নয়, পুরো ইন্ডাস্ট্রির উন্নতির প্রশ্ন।
ওয়াহিদ সুজন: খুবই ইন্টারেস্টিং ও প্যাথেটিক তথ্য। এখন অবশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে নিজেদের বড় দেখানোর জন্য হিসাব-প্রকাশ না করেও উপায় নেই। আমার একটা বিষয় কৌতুহল ছিল— অনলাইন ট্র্যাক করে না হয় মাল্টিপ্লেক্স অকুপেন্সি অনুসারে একটা ডাটা পাচ্ছি। যা রিয়েলিটির কাছাকাছি। কিন্তু রেন্টাল বা লভ্যাংশ ভাগাভাগির সিস্টেম, মানে যেটা সিঙ্গেল স্ক্রিনে, সেখানকার আয়ের তথ্য কীভাবে দিচ্ছে। একটা ফিক্সড অ্যামাউন্টে যদি সিনেমা হল দেয়, সেখানে কত টাকার টিকিট বিক্রি হলো, সেই তথ্যে প্রযোজকের লাভ-ক্ষতি কীভাবে বোঝা যায়?
ফাহিম মুন্তাছির: আমি শুনলাম প্রযোজকেরা এবার আলাদা মনিটরিং টিম রেখেছে, সিঙ্গেল স্ক্রিনের শোগুলোতে দর্শক কেমন হচ্ছে সেটি দেখার জন্য। যদিও জানি না তারা সবগুলো সিনেমাহল কভার করতে পেরেছে কিনা, বা প্রতিদিন ট্র্যাক করছে কিনা।
প্রযোজকদের পক্ষে সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে প্রকৃত আয় বোঝা বর্তমান ব্যবস্থায় সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। যেহেতু এখানে ফিক্সড রেন্টাল মডেল প্রচলিত, প্রযোজক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টে সিনেমাহলকে চলচ্চিত্র ভাড়া দেন— টিকেট বিক্রির পরিমাণ নির্বিশেষে। ফলে সিনেমাহল কত টিকেট বিক্রি করল বা আসল আয় কত হলো, তার সঠিক হিসাব প্রযোজকের হাতে পৌঁছায় না। অনেক ক্ষেত্রে হল মালিকরা নিজেদের সুবিধামতো হিসাব দেন, যা প্রায়ই বাস্তবতার সাথে মেলে না।
আমার মনে হয় প্রযোজকরা মূলত মাল্টিপ্লেক্সের আয় এবং সিঙ্গেল স্ক্রিনের আনুমানিক রেসপন্স দেখেই লাভ-ক্ষতির হিসাব কষেন। বর্তমানে এটি একটি বড় সমস্যা, যা পুরো ইন্ডাস্ট্রির স্বচ্ছতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই সিস্টেমে প্রযোজকের লাভ সঠিকভাবে বোঝার একমাত্র উপায় হলো থিয়েটার মালিকদের সাথে সরাসরি ভালো সম্পর্ক এবং মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। নতুন প্রযোজকরা কখনোই এটি পারবে না, এছাড়া কাজটি সময়সাপেক্ষ এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পুরোপুরি নির্ভরযোগ্যও নয়। হল প্রতিনিধিরা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পান না, তাই তাদের অনেকে এই কারচুপির সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। আবার তাদের মধ্যে যেহেতু সততার অভাব রয়েছে, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করলেও যে তারা কারচুপিতে জড়িত হবে না, এই নিশ্চয়তাও পাওয়া যাচ্ছে না। তো সবমিলিয়ে আমি মনে করি না তারা এতো দ্রুত সঠিক হিসাবটি পাবে। হলগুলো যদি ই-টিকিটিং ও একটি সেন্ট্রাল সার্ভারের সিস্টেমে যায় তখন হয়তো এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।
ওয়াহিদ সুজন: তবে এই যে আয়ের তথ্য পাবলিক করা, এটা নতুন দিনের সিনেমা হলের কারণে সম্ভব। তবে এখনো আমরা মাল্টিপ্লেক্স কালচার বলতে স্টার সিনেপ্লেক্সকে বুঝছি। তাদের কৃতিত্ব তো আছে, আবার একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে হুটহাট টিকিটের দাম বাড়ানোর বিষয়টা তো রয়েছে। আমরা এর আগে একবার কথা বলছিলাম। তখন দেখা গেল ঈদের ২০ দিনে এবার স্টার সিনেপ্লেক্সের বাংলা সিনেমা থেকে আয় ১৬ কোটি টাকার কম-বেশি। মাঝে হলিউড সিনেমা চললেও পরে দর্শকচাপে এগুলো ছিটকে পড়ে। তো, ১৬ কোটি হিসাব কিন্তু ২২ স্ক্রিনে। যেটা সিঙ্গেল স্ক্রিনের হিসেবে হিউজ। এখন যদি স্ক্রিন ১০০টা দাঁড়ায় কী হবে অবস্থা?
ফাহিম মুন্তাছির: জ্বী, স্টার সিনেপ্লেক্সের বর্তমান একচেটিয়া অবস্থান এবং টিকিট মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ সঠিক। তবে এটাও বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে হবে, তারাই একমাত্র সিরিয়াসলি ২০১৯ সাল থেকে মাল্টিপ্লেক্স চেইন গড়ে তুলেছে, বাকিরা কেউ বিগত ৬ বছরে তাদের প্রতিযোগী হওয়ার চেষ্টাই করেনি। এ জন্যে বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে তারা টিকেটমূল্য প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছে।
বিএমআরের হিসাব মতে, গতকাল (২৪ এপ্রিল) পর্যন্ত ২৫ দিনে ঈদের চলচ্চিত্রগুলো স্টার সিনেপ্লেক্সের ২২টি স্ক্রিনে গ্রোস আয় করেছে ১৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এই ২২ স্ক্রিনে মোট শো চলেছে ২ হাজার ২৫টি, গড়ে দৈনিক ৮১ শো, যা বলা যায় প্রায় ২০টি সিঙ্গল স্ক্রিনের সমান। মাত্র ৭টি মাল্টিপ্লেক্স ২০টি সিঙ্গল স্ক্রিনের চাহিদা পুরণ করছে।
এই হিসেবে মোটামুটি যদি আমরা সারাদেশে ৩০-৩৫টি মাল্টিপ্লেক্স পাই তাহলেই ১০০ স্ক্রিন গড়ে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ বর্তমানে যা অবস্থা তার তুলনায় তিনগুণ মাল্টিপ্লেক্স লাগবে। তাহলে চলচ্চিত্রগুলোর ইনকামও বাড়বে। তবে এখানে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি—
প্রথমত, শুধু মাল্টিপ্লেক্স বাড়ালে তো হবে না। মাল্টিপ্লেক্স বাড়লে মাল্টিপ্লেক্সে চালানোর মতো পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন সিনেমাও লাগবে। সেটি নিশ্চিত করতে হবে। নয়তো একই সময়ে অনেক স্ক্রিনে একই সিনেমা চালু রেখে আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। এখানে প্রযোজকদের নতুন ও বৈচিত্র্যময় কনটেন্ট তৈরি করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, ঢাকার মাল্টিপ্লেক্স থেকে যতটা আয় হয়, ঢাকার বাইরের মাল্টিপ্লেক্সগুলো থেকে ততটা আয় হয় না। স্টার সিনেপ্লেক্সের উচ্চ টিকিটমূল্য এখানে একটি অন্যতম বড় ইস্যু। তো ঢাকার বাইরে যারাই মাল্টিপ্লেক্স করবেন, ভালোভাবে হিসাব কষে ক্যালকুলেটিভ রিস্ক নিতে হবে। অবশ্যই টিকিটমূল্য কমাতে হবে, রাখতে হবে ২০০-২৯৯ টাকার মধ্যে, নয়তো ছুটির দিন ছাড়া দর্শক সমাগম করা মুশকিল।
ওয়াহিদ সুজন: আমার একটা বিষয়ে মনে পড়ছে, ৮০-৯০ এর দশকে যখন বাংলা সিনেমা জমজমাট ছিল তখন দেখা যেত, অনেক সিনেমা প্রথম সপ্তাহে ঢাকার বাইরের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোয় মুক্তি পায়। এখানে হিট হওয়ার পরে ঢাকাতে এসে হিট হয়। কিন্তু এখন দর্শকের রুচি ও শ্রেণি সম্ভবত পাল্টে গেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ছবিগুলো ঢাকাতে হিট হচ্ছে সেগুলোই ঢাকার বাইরের দর্শকরা দেখছে। এমনকি বিদেশে বাংলা সিনেমার দর্শক খেয়াল করলে দেখবেন, যে ছবিগুলো ঢাকায় হিট হচ্ছে উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় ভালো ব্যবসা করছে। আর ঢাকা মানেই এখন মাল্টিপ্লেক্স। এর মানে হচ্ছে এখন মাল্টিপ্লেক্সকে অনেক বড় ফ্যাক্টর হিসেবে ধরা দিচ্ছে।
ফাহিম মুন্তাছির: জ্বী, অবশ্যই মাল্টিপ্লেক্স একটি বড় ফ্যাক্টর। আমি সিঙ্গেল স্ক্রিনের বিপক্ষে নই, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সিঙ্গেল স্ক্রিনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটাই সত্যি যে, মাল্টিপ্লেক্সই একটি চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ। স্বল্পসময়ের মধ্যে যদি কোনো সিনেমা সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের কাছে পৌছাতে চায়, তবে মাল্টিপ্লেক্সের থেকে বেটার অপশন নেই। এছাড়া মাল্টিপ্লেক্স শুধু একটি প্রদর্শন মাধ্যমই নয়, বরং এটি এখন সিনেমার বাণিজ্যিক সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে কাজ করছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো মাল্টিপ্লেক্স একটি বিশেষ শ্রেণি দর্শকদের টার্গেট করে— যারা শুধু সিনেমা দেখে না, বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সিনেমার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই পরিবর্তনটি ইঙ্গিত দেয় যে, এখন সিনেমার সাফল্য নির্ভর করছে শহুরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত দর্শকদের রুচি ও অভ্যাসকে কীভাবে সফলভাবে ধারণ করা যায় তার ওপর।
ওয়াহিদ সুজন: টিকিটের দাম ব্যাপারটা এত বড় ফ্যাক্টর এখনো মনে করি। কারণ ঢাকায় আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখানে অবসর বা বন্ধুদের সময় কাটানোর জন্য রেস্টুরেন্ট ছাড়া বেশি অপশন নাই। এমনও দেখেছি সিনেমা দেখছে কিন্তু দর্শকের মনোযোগ থাকে আড্ডা-গল্পে। এই বিষয়টা যদি মাথায় রাখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঢাকার বাইরের দর্শকের সামনে কিন্তু অবসর কাটানোর অপশন আছে। আসলেই সবাইকে একনিষ্ঠ সিনেমার দর্শক ভাবাও ঠিক না। ফলে ঢাকার বাইরে আসলে মাল্টিপ্লেক্স যখন বাড়া দরকার তেমনি টিকিটের দামও কম থাকা উচিত। নইলে দর্শক বাড়ানো মুশকিল। আরো খেয়াল করলে দেখবেন, মাল্টিপ্লেক্সের কারণে কিন্তু ‘চক্কর ৩০২’ বা ‘প্রিয় মালতী’র মতো ছবি কোটি খানিক গ্রসের কাছাকাছি যেতে পারছে। ‘হাওয়া’ বা ‘আয়নাবাজি’র মতো ছবির যে জোয়ার তার পেছনেও মাল্টিপ্লেক্সের একটা ভূমিকা আছে। এগুলো কিন্তু (প্রচলিত অর্থে) ভিন্ন রুচি …
ফাহিম মুন্তাছির: জ্বী, শতভাগ একমত। আমাদের এখনো অনেক দর্শক সিনেমাহলমুখী করা বাকি, যারা একসময় সপ্তাহে অন্তত একটা সিনেমা পরিবার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেখতো। কিছু দর্শক ছিল যারা স্কুল-কলেজ পালিয়ে সপ্তাহে একটি সিনেমা দেখতো। আমাদের সেই দর্শকদের সিনেমাহলে যাওয়ার অভ্যাসটি, ভালো পরিবেশ ও পর্যাপ্ত ভালো চলচ্চিত্র উপহার না দিতে পেরে, আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। তাই অবশ্যই ঢাকার বাইরে কম টিকিটমূল্যের মাল্টিপ্লেক্স দরকার, আর তার সাথে নিয়মিত সিনেমাহলে চালানোর মতো পর্যাপ্ত চলচ্চিত্র দরকার।
ওয়াহিদ সুজন: আপনি একসময় ঢাকা ও আশপাশের সিনেমা হল নিয়ে সরেজমিনে কাজ করেছেন, সেই বিষয়ে লেখাগুলো বিএমডিবিতে প্রকাশ করেছেন। যাতে দর্শকরা সহজে ইনফরমেশন পেতে পারে। সেটাও কয়েক বছর আগের কথা। এই যে সিনেমা হল ধরে ধরে অভিজ্ঞতা নেয়া, সব নিশ্চয় ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতা ছিল না। ওই অভিজ্ঞতা আর এখনকার সময় মিলিয়ে কী বলবেন। বিশেষ করে সিঙ্গেল স্ক্রিনের যে অবস্থা ছিল, এর পতন মানে এখন বেশিরভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কে দায়ি?
ফাহিম মুন্তাছির: ধন্যবাদ। আমি ২০১৯ সালে ঢাকা, সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এই চার শহরের প্রায় সবগুলো সিনেমাহল সরেজমিনে গিয়ে দেখেছিলাম। অল্পকিছু সিনেমাহল ছিল যেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সেগুলো আমি সরাসরি দেখতে পারিনি। কিন্তু আমি সিনেমাহল দেখার জন্য ঢাকা থেকে কালিয়াকৈর গিয়েছি, জয়দেবপুর গিয়েছি, কাঁচপুর ব্রিজ ক্রস করে ভুলতা-গাউছিয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছি, চাষাড়া গিয়েছি।
আমি ওই সময়েই সবগুলো সিনেমাহল আজীবনের জন্য বন্ধ হবে, এমন অবস্থায় গিয়ে পেয়েছি। সেই সময়টি ছিল করোনা আসার আগেই, করোনা ছিল সিনেমাহল বন্ধ করার একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সিঙ্গেল স্ক্রিন বন্ধ হওয়ার প্রথম কারণ আমার মনে হয়, তারা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। তারা নব্বইয়ের শেষ থেকে করোনা আসার আগ পর্যন্ত গ্লোবাল মার্কেট ট্রেন্ড থেকে অনেকবেশি পিছিয়ে ছিল। শূন্য দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতের সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলো ডিজিটালাইজড হওয়া শুরু হয়। অথচ আমরা সেটি বাস্তবায়ন করতে সময় নিয়েছি ২০১২ সাল পর্যন্ত! ২০০০-২০০৬ এই সময়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পুরোপুরি বি-গ্রেড সিনেমা নির্ভর হয়ে গিয়েছিল। এতোটাই নির্ভরতা ছিল যে টপ লেভেলের স্টারদের সিনেমাও একদিন ভালো ওপেনিং নিয়ে এরপর বি-গ্রেড সিনেমার সাথে পেরে উঠতো না। সেই অশ্লীল সিনেমা আমরা যখন বন্ধ করলাম, তখনই উচিত ছিল আমাদের ডিজিটাল চলচ্চিত্রের দিকে চলে যাওয়া। এখানে আমরা প্রায় ছয় বছর দেরি করেছি, সময়ের থেকে এগিয়ে ভাবতে পারিনি।
দ্বিতীয়ত, সিনেমাহলগুলোর মালিক যারা, তারা সবাই ওইসব এলাকার গণ্যমান্য স্থানীয় ব্যক্তি, বয়সের দিক থেকে এখন তারা প্রবীণ। আশির দশকে তারা যে আগ্রহ নিয়ে সিনেমাহল চালিয়েছেন, তাদের পরের জেনারেশনের মধ্যে সিনেমাহল চালানোর সেই আগ্রহ নেই। সিনেমাহলগুলো থাকে হল ম্যানেজারের কন্ট্রোলে। তারা মালিক থেকে সিনেমাহল ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছে। এজন্যে সিনেমাহল যে সংস্কার করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সর্বোপরি ভালো একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বহন করে, এটি তারা কখনোই উপলব্ধি করেনি। এখনো তারা নিজেরা বুঝে না যে কেন তাদের দর্শক কমে গেলো।
ওয়াহিদ সুজন: গত কয়েক দিনে অনেক কথাই বলে ফেললাম আমরা। আশা করি সামনেও আরো কথা হবে। আমি যেটা মিস করি ফাহিম মুন্তাছিরের লেখার রিভিউ। খুবই পেশাদারী ভঙ্গিতে সিনেমার বিভিন্ন বিভাগ ধরে লেখা হতো। যাই হোক জানতে চাই, বাংলা মুভি রিভিউ বা বিএমআরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
ফাহিম মুন্তাছির: অনেক শুকরিয়া। আমিও আমার এই কাজটি (রিভিউ লেখা) অনেক মিস করি। ব্যক্তিগত ব্যস্ততার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আমি আমার পছন্দের কাজটি করতে পারছি না। কোনো চলচ্চিত্রের রিভিউ লিখতে গেলে, সেই চলচ্চিত্র দেখা থেকে শুরু করে রিভিউ গোছানো পর্যন্ত, সবমিলিয়ে আমার প্রায় দুইদিন সময় লাগতো। এখন যখন দেখতে পাচ্ছি, চলচ্চিত্রের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানকার গ্যাপগুলো ফিলআপ করা জরুরি, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি আপাতত। তবে আমার ইচ্ছা আছে, খুব শিগগিরই আমি আমার চিরচেনা ঢঙ্গে নিয়মিত চলচ্চিত্রগুলোর রিভিউ দেয়া শুরু করব।
এর পাশাপাশি যদি আমাদের বক্স অফিস ডেটা নিয়ে বলি,আমার ইচ্ছা আছে যে ডেটাগুলো আমরা এখন দিতে পারছি না, সেই ডেটাগুলো ভবিষ্যতে সঠিকভাবে দেয়ার। অবশ্যই আমরা আনুমানিক কিছু দিবো না, চাইলে আমরা এবারই সেটা করতে পারতাম। আমরা প্রথমে ঢাকার সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো দিয়ে কাজ শুরু করবো, সবকিছু গুছিয়ে এরপর আমাদের পেইজের মাধ্যমে সবাইকে বিস্তারিত জানাবো। আমাদের যারা ফলো করছেন, তাদের ভালোবাসা ও সাপোর্টের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তো তাদের ভরসা আমি রাখতে চাই। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি একটি বক্স অফিস তৈরি করতে চাই।